ইয়ারার তীরে মেলবোর্ন [০১] [০২] [০৩] [০৪] [০৫] [০৬] [০৭] [০৮] [০৯] [১০][১১][১২][১৩][১৪][১৫][১৬][১৭]
১৮
২৬ জুলাই ১৯৯৮ রবিবার
ফিজিক্স রিসার্চ লাইব্রেরি
লাইব্রেরিয়ান কমলা লিকাম্জি যেদিন আমাকে রিসার্চ লাইব্রেরির কোথায় কী আছে দেখিয়েছিলেন, সেদিন কাচের দেয়াল ঘেরা এই স্পেশাল রিডিং রুমটা দেখিয়ে বলেছিলেন “বাইরের শব্দ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন যদি হয়ে যেতে চাও তবে এই রুমে ঢুকে পড়ো”। আজ সকাল দুপুর ইয়ারার তীরে কাটিয়ে এসে একটু আগে ঢুকে পড়েছি এখানে- শব্দ এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পাঠকক্ষে।
ছুটির দিন। লাইব্রেরিতে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। এ রুমে ঢোকার পর বাইরের কোন শব্দও শোনা যাচ্ছে না। সারি সারি ছাদছোঁয়া তাকভর্তি বইয়ের মাঝখানে এসে কী যে ভালো লাগছে। এখানে আসার সুযোগ না পেলে হয়তো কোনদিনই জানতাম না যে ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরিগুলো এরকমও হতে পারে।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় লাইব্রেরি থেকে একটা বইও ধার করতে পারিনি কখনো। বই বাসায় নিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা, বইয়ের তাক থেকে নিজের হাতে বই বাছাই করার সুযোগও ছিল না। লাইব্রেরিতে বসে বই পড়ার জন্যও কত ঝামেলা করতে হতো। নিজের বই-পত্র ব্যাগ সব লাইব্রেরির বাইরে রেখে শুধুমাত্র কাগজ কলম নিয়ে লাইব্রেরিতে ঢুকতে হতো। তারপর বইয়ের রেফারেন্স কার্ড দেখে কল নাম্বার লিখে লাইব্রেরি কার্ড সহ কাউন্টারে জমা দিলে লাইব্রেরির কর্মচারীদের কেউ একজন ধীরে সুস্থে তাক থেকে বই খুঁজে নিয়ে আসতেন। বেশির ভাগ সময়েই দেখা যেতো বই পাওয়া যাচ্ছে না। বলা হতো কোন শিক্ষক হয়তো ইস্যু করে নিয়ে গেছেন। কোন নির্দিষ্ট লেখকের বই পাওয়া না গেলে একই বিষয়ের ওপর অন্য কোন লেখকের বই যে একটু খুলে দেখবো সে উপায়ও ছিল না।
মাস্টার্সের শেষের দিকে নতুন লাইব্রেরি ভবন তৈরি হবার পর অবস্থার সামান্য উন্নতি হলো। না, বই ধার করার সুযোগ নয়, তাক থেকে নিজের হাতে বই বাছাই করার সুযোগ হলো। কিন্তু তাতে নতুন সমস্যা দেখা দিলো। বইয়ের মাঝখান থেকে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উধাও হয়ে যেতে শুরু করলো। অভিযোগ কাকে করবো- বইয়ের পাতা যারা কাটছে তারাও তো আমার মত শিক্ষার্থী। অর্থনৈতিক দারিদ্র্যের কারণে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে প্রচুর বই নেই, আর মানসিক দৈন্যতার কারণে আমরা বইয়ের পাতা কাটি।
মেলবোর্ন ইউনিভার্সিটির যে কোন শিক্ষার্থী এক সাথে তিরিশটা, আর গবেষণা শিক্ষার্থী এক সাথে ষাটটা বই ধার করতে পারে। এই ইউনিভার্সিটির বিশটা লাইব্রেরির মোট তিরিশ লাখ বইয়ের মধ্যেও যদি কোন একটা দরকারি বই না থাকে- তবে লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষ বইটি কেনার ব্যবস্থা করে। একেবারে শূন্য থেকে হঠাৎ এত বেশি সুযোগ হাতে এসে গেলে আনন্দের সাথে কিছুটা কষ্ট লাগাও স্বাভাবিক। সুখের দিনেই তো দুখের বাতাস বুকের কপাট নাড়ায়।
কাল কয়েকটা বই নিয়ে এসেছিলাম বিলিউ লাইব্রেরি থেকে। অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাস কিছুই তো জানি না। বই পড়ে যদি কিছুটা জানা যায়। কিন্তু জানোই তো- পৃথিবীর বেশির ভাগ ইতিহাস পক্ষপাতদুষ্ট। একই ঘটনার কত ভিন্ন ভিন্ন বিশ্লেষণ, কত ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। আপাততঃ ঘটনা জানা যাক। বিশ্লেষণ পরে জানলেও চলবে।
পৃথিবীর অনেক জাতিকেই স্বাধীনতার জন্য রক্ত দিতে হয়েছে। তিরিশ লাখ শহীদের রক্তে আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা পেয়েছি। অস্ট্রেলিয়ার সে রকম গর্ব করার মত কোন স্বাধীনতার ইতিহাস নেই। শুরু থেকেই এটা ব্রিটিশদের কলোনি ছিল। স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার একশ’ বছর পার হয়ে গেছে অথচ এখনো ব্রিটেনের রাণীকে এখানেও রাণীর সম্মান দেয়া হয়। তবে অস্ট্রেলিয়ার ‘অস্ট্রেলিয়া’ হয়ে ওঠার ইতিহাস বেশ মজার।
“টেরা অস্ট্রালিস নন্ডাম কগ্নিটা (terra australis nondum cognita)” বা ‘দক্ষিণ মেরুর অচিনভূমি’ হিসেবে ম্যাপের নিচের দিকে অবহেলায় পড়েছিল পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন মহাদেশটি। খ্রিষ্টের জন্মের চারশ’ বছর আগেই মানুষ এই মহাদেশটার অস্তিত্ব অনুমান করেছিল। সাধারণ যুক্তিবোধ থেকেই ভেবেছিল যে উত্তর গোলার্ধে যখন এতগুলো দেশ- এত বড় ভূখন্ড, ভারসাম্য রক্ষার জন্য দক্ষিণ গোলার্ধেও সে পরিমাণ ভূমি থাকবেই।
ল্যাটিন শব্দ অস্টার (auster) মানে দক্ষিণ। অস্টার থেকে অস্ট্রাল – দক্ষিণ মেরু। শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে গেছে অথচ সভ্যতার আঁচ লাগেনি এই টেরা অস্ট্রালিস মানে দক্ষিণ মেরুর অচিনভূমিতে।
আনুমানিক ১৫৩৬ থেকে ১৫৪৬ সালের মধ্যে আঁকা একটি ম্যাপ ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রাখা আছে। সেখানে দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি এই ভূ-খন্ড চিহ্নিত হয়েছে ‘জাভা লা গ্রঁদ (Java La Grande)’ বা ‘বৃহৎ জাভা’ নামে। ইন্দোনেশিয়ার কয়েক হাজার দ্বীপের বেশ কিছু আবিষ্কৃত হয়ে গেছে ততদিনে। জাভা দ্বীপের নামানুসারেই ‘বৃহৎ জাভা’।
অস্ট্রেলিয়া নামটা এসেছে ‘অস্ট্রিয়ালিয়া ডেল ইস্পিরিতা সান্তো (Austrialia del Espirita Santo)’ বা ‘সাউদার্ন ল্যান্ড অব হলি গোস্ট’ থেকে। (বাংলায় ‘হলি গোস্ট’-এর সঠিক প্রতিশব্দ কী হবে বুঝতে পারছি না। আমাদের সংস্কৃতিতে তো ‘পবিত্র ভূত’ বা ‘পবিত্র গাভী’র আনাগোনা খুব একটা নেই।) পর্তুগিজ নাবিক ফার্নান্দেজ ডি কুইরোস সর্বপ্রথম এই নামটি ব্যবহার করেন ১৬০৬ সালে। ডি কুইরোস কাজ করতেন স্পেনের রাজা তৃতীয় ফিলিপের অধীনে। রাজা ফিলিপের জন্ম হয়েছিল অস্ট্রিয়ায়। ফার্নান্দেজ ডি কুইরোস রাজাকে খুশি করার উদ্দেশ্যেই টেরা অস্ট্রালিসকে ‘অস্ট্রিয়ালিয়া’ নাম দিয়েছিলেন। রাজা যে খুশিই হয়েছিলেন তা বোঝা যায়। ডি কুইরোসকেই দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল অস্ট্রিয়ালিয়া খুঁজে বের করার।
১৬০৬ সালে পাল তোলা জাহাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন ডি কুইরোস। প্রশান্ত মহাসাগরের অনেক অজানা দ্বীপ আবিষ্কৃত হলো। কিন্তু ‘অস্ট্রিয়ালিয়া’ আবিষ্কার করার সুযোগ পান নি ডি কুইরোস। মাসের পর মাস পানিতে ভাসতে ভাসতে অসুস্থ হয়ে পড়তে শুরু করলো ডি কুইরোসের জাহাজের শ্রমিকেরা। শারীরিক অসুস্থতা থেকে মানসিক অস্থিরতা, অসন্তোষ। বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়লো জাহাজ জুড়ে। সেকেন্ড ইন কমান্ড লুই ভেজ ডি টরেস শ্রমিকদের পক্ষ নিয়ে কথা বলতেই প্রবল ঝগড়া হয়ে গেল ডি কুইরোসের সাথে। প্রচন্ড রেগে গিয়ে ক্যাপ্টেন ডি কুইরোস কাউকে কিছু না বলে ছোট একটা জাহাজে চড়ে চলে যান পেরু হয়ে স্পেনের দিকে। ক্যাপ্টেন ডি টরেস কয়েকদিন অপেক্ষা করলেন ডি কুইরোসের জন্য। কিন্তু ডি কুইরোস ফিরলেন না।
ডি টরেস জাহাজ নিয়ে নিউ গিনির উত্তর দিক দিয়ে এগোবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু এমন ঝড়-বাতাস শুরু হলো যে তিনি গতিপথ বদলাতে বাধ্য হলেন। নিউ গিনির দক্ষিণ দিক দিয়ে ফিরে আসার সময় কেইপ ইয়র্কের অংশ বিশেষ দেখা গিয়েছিল, কিন্তু ক্যাপ্টেন টরেস ভেবেছিলেন ওটা ছোটখাট কোন দ্বীপ। তাই খুব একটা মনযোগ দেননি সেদিকে। দিলে হয়তো তিনিই হতে পারতেন উত্তরপূর্ব অস্ট্রেলিয়ার আবিষ্কারক। (কেইপ ইয়র্ক অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ডের অংশ)।
ক্যাপ্টেন ডি টরেস নিউগিনির দক্ষিণে প্রায় শ’দুয়েক ছোট ছোট দ্বীপ দেখেছিলেন। ডি টরেসের অভিযানের ১৮০ বছর পর ব্রিটিশ সরকার এই দ্বীপগুলোর নাম রাখে টরেস স্ট্রেইট আইল্যান্ড। দ্বীপগুলো এখন অস্ট্রেলিয়ার অধীনে।
ইউরোপিয়ানদের মধ্যে ডাচরাই প্রথম পা রাখেন অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে। ১৬০৬ সালে ক্যাপ্টেন উইলেম জ্যান্স, তারপর ১৬১৬ সালে ক্যাপ্টেন ডার্ক হার্গট ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার উত্তর-পশ্চিম সমুদ্রতীরে নোঙর ফেলেন। পরবর্তী কয়েক দশক ধরে আরো অনেক ডাচ জাহাজ এসেছে এখানে। এ কারণেই অস্ট্রেলিয়া ‘নিউ হল্যান্ড’ নামে পরিচিত ছিল পরবর্তী অনেক বছর।
জনমনুষ্যহীন এত বড় দ্বীপটির বেশিরভাগ অংশ তখনো অনাবিষ্কৃত। ইস্ট ইন্ডিজের ডাচ গভর্নর জেনারেল এন্থনি ফন ডাইমেন ব্যাপক পরিসরে দক্ষিণ গোলার্ধে অভিযান চালানোর পরিকল্পনা নেন। কমান্ডার নিযুক্ত হলেন ক্যাপ্টেন আবেল তাসমান। ১৬৪২ সালের ১৪ আগস্ট তাসমানের জাহাজ জাকার্তা থেকে দক্ষিণ দিকে যাত্রা শুরু করে। দক্ষিণ মেরুর যতটা কাছাকাছি যাওয়া যায়। প্রায় তিন মাস ধরে চলার পর ২৪ নভেম্বর দুটো পাহাড়চূড়া দেখতে পেলেন ক্যাপ্টেন তাসমান। কিন্তু এমন ঝড়-তুফান চলছিলো সে সময়- অস্ট্রেলিয়া রয়ে গেল চোখের আড়ালে। তাসমান চলে গেলেন আরো প্রায় পাঁচশ’ কিলোমিটার দক্ষিণে ছোট্ট দ্বীপটির দিকে। নোঙর করলেন সেখানে। ক্যাপ্টেন তাসমান তাঁর গভর্নর জেনারেলের নামে দ্বীপটির নাম রাখলেন ‘ডাইমেন’স ল্যান্ড’। (আরো দু’শ বছর পর ১৮৫৬ সালে ক্যাপ্টেন তাসমানের সম্মানে দ্বীপটির নাম রাখা হয় তাসমানিয়া।)
তাসমানিয়া আবিষ্কারের আটদিন পর আবিষ্কৃত হলো আরো আড়াই হাজার কিলোমিটার দক্ষিণের দ্বীপ নিউজিল্যান্ড। এর দু’বছর পর ক্যাপ্টেন তাসমান আবারো এসেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার দিকে। ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার উত্তর-পশ্চিম তীর ধরে ঘুরে গেছেন।
অস্ট্রেলিয়ার মূল ভূ-খন্ডে প্রথম যে ইংরেজ পা রাখেন বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়- তিনি হলেন একজন দুর্ধর্ষ নাবিক উইলিয়াম ড্যাম্পিয়ার। জলদস্যুদের দেখলেই তাড়া করতেন ড্যাম্পিয়ার। ফলে তাঁর শত্রুর সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়ছিল। শেষে অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে ড্যাম্পিয়ার নিজেই শত্রুদের কাছ থেকে পালিয়ে যেতে চাইলেন যত দূরে যাওয়া সম্ভব। একটানা জাহাজ চালিয়ে চলে এসেছিলেন ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার ব্রুম-এর কাছে। প্রায় দু’মাস ছিলেন সেখানে। অস্ট্রেলিয়ার অদ্ভুত সব জীবজন্তু গাছ-পালা দেখে অবাক হয়েছেন। পেটের থলিতে বাচ্চা নিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলা এমন অদ্ভুত প্রাণী আগে দেখা তো দূরের কথা শোনেনও নি কখনো।
ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার রুক্ষ আবহাওয়া সহ্য হয়নি ড্যাম্পিয়ারের। পথে শত্রুর হাতে পড়ার ভয় থাকা সত্ত্বেও ফিরে গেলেন ইংল্যান্ডে। ফিরে গিয়ে লিখে ফেললেন তাঁর ভ্রমণকাহিনি “এ নিউ ভয়েজ রাউন্ড দি ওয়ার্ল্ড”। লেখাটি প্রকাশিত হবার পর ব্রিটিশ সরকার ক্যাপ্টেন ড্যাম্পিয়ারকেই দায়িত্ব দিলো নতুন করে ‘নিউ হল্যান্ড’ অভিযানের। ১৬৯৯ সালে পুরো চার মাস ধরে অভিযান চালিয়েও খুব বেশি নতুন কিছু আবিষ্কার করতে পারলেন না ড্যাম্পিয়ার।
এরপর বছরের পর বছর ধরে অনেক অভিযান চলেছে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার প্রধান অংশ আবিষ্কৃত হয় আরো সত্তর বছর পর। ১৭৭০ সালে দক্ষিণের কলম্বাস নামে খ্যাত ক্যাপ্টেন জেম্স কুক। তাঁর জাহাজ ‘এনভেভার’ নোঙর করলো ‘বোটানি বে’র সৈকতে। গ্রেট ব্রিটেনের পতাকা উড়িয়ে জায়গাটার নাম রাখা হলো নিউ সাউথ ওয়েল্স। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ায় আনুষ্ঠানিক ব্রিটিশ রাজ শুরু হয় আরো কয়েক বছর পর। জেম্স কুক্কে বীরের সম্মান দেয়া হয় অস্ট্রেলিয়ায়। ক্যাপ্টেন কুকের কটেজ আছে মেলবোর্নেই। যেতে হবে একদিন।
১৭৭৬ সালে আমেরিকা স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১৭৮৩ সালে যুদ্ধ শেষ হবার পর উত্তর আমেরিকার সবগুলো কলোনি হারিয়ে ব্রিটেনের অবস্থা খারাপ। অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে সাথে সামাজিক অবস্থাও ভীষণ খারাপ হতে শুরু করলো। চুরি ডাকাতি বেড়ে গেলো। স্কটল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডের রাজনৈতিক সমস্যা সহ আরো নানারকম অস্থিরতা তো আছেই। কয়েক মাসের মধ্যেই ব্রিটেনের কারাগারগুলোতে জায়গার সংকট দেখা দিলো। এতদিন বছরে এক হাজারেরও বেশি কয়েদীকে পাঠিয়ে দেয়া হতো ভার্জিনিয়া ও মেরিল্যান্ডে। ওগুলো এখন আমেরিকার দখলে।
কয়েদী সমস্যার সমাধানের জন্য ব্রিটেন সরকার উঠেপড়ে লাগলো। অস্ট্রেলিয়া হয়ে উঠলো ভার্জিনিয়া ও মেরিল্যান্ডের বিকল্প। খুন-খারাবির মত জঘন্য অপরাধীদের নিয়ে তেমন কোন সমস্যা ছিল না। কারণ তাদের ধরে ফাঁসিতে ঝোলানো হতো। সমস্যা ছিলো ছোটখাট অপরাধী আর রাজনৈতিক বন্দীদের নিয়ে। তাদের সবাইকে অস্ট্রেলিয়ায় পাঠিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো।
১৭৮৮ সালের ২৬ জানুয়ারি ক্যাপ্টেন আর্থার ফিলিপের নেতৃত্বে ১৪৮৭ জন কয়েদী ভর্তি এগারোটি জাহাজ এসে ভিড়লো সিডনি কোভে। আট মাসেরও বেশি সময় লেগেছে তাদের ব্রিটেন থেকে অস্ট্রেলিয়ায় এসে পৌঁছাতে। কয়েকজন সৈন্য আর কিছু অফিসার ছাড়া বাকি সবাই চোর-ডাকাত। পরের বছরগুলোতে অনেক স্কটিশ আর আইরিশ রাজবন্দীকেও পাঠিয়ে দেয়া হয় অস্ট্রেলিয়ায় কোন রকম বিচার ছাড়াই।
তারপর দুশ’ বছর ধরে কীভাবে নানা জাতির সমন্বয়ে ধীরে ধীরে একটা নতুন দেশ নতুন অস্ট্রেলিয়া তৈরি হয়েছে সে কাহিনি এখনো পড়া হয়নি। কাল রাতে আরো কিছুটা পড়তে পারতাম, কিন্তু ডেভিডের কারণে হলো না। ডেভিডের কথা কি তোমাকে বলেছিলাম?
ফিলের ছেলে ডেভিডের সাথে দু’একবারের বেশি দেখা হয়নি। প্রথমবার দেখেই মনে হয়েছিল সে ড্রাগ নেয়। আর সিগারেট তো সারাক্ষণ মুখে লেগেই থাকে। মনে মনে তাকে এড়িয়ে চলতে চেয়েছি। কিন্তু কাল রাত সাড়ে ন’টার দিকে দরজায় টোকা পড়ার পর দরজা খুলে দেখি সিগারেট মুখে দাঁড়িয়ে আছে ডেভিড আর তার গায়ের সাথে লেপ্টে আছে একজন তরুণী।
“হাই প্রাডিব, হাউ ইউ ডুয়িং?”
“গুড ডেভিড। হাউ আর ইউ?”
“গুড। মিট জোয়ানা, মাই গার্লফ্রেন্ড। এন্ড জোয়ানা -হি ইজ প্রাডিব”
ডেভিডকে যতই এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি, ভদ্রতার দায় তো এড়াতে পারি না। ভদ্রতার দাঁত বের করে জোয়ানার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম। জোয়ানা আমার হাতটা টেনে নিয়ে হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে ধরে দু’গালে চুমু খেলো। এটা হয়তো এদেশের সংস্কৃতির অংশ। কিন্তু আমি আশাও করিনি জোয়ানা এরকম কিছু করবে। ভালো করে তাকালাম জোয়ানার দিকে। মাধুর্য বলতে যা বোঝায় তার কিছুই নেই তার মুখে। সামান্য গোল মুখ আর বিড়ালের চোখের মত চোখ। উচ্চতায় প্রায় আমার সমান। একটা ব্যাপারই জোয়ানার মধ্যে বড় বেশি স্পষ্ট- তা হলো শরীর। ডেভিডের একটা হাত জোয়ানার কোমর জড়িয়ে রেখেছে।
“প্রাডিব খুব ভালো ছেলে। ইউনিভার্সিটিতে পড়তে এসেছে ইন্ডিয়া থেকে”
ডেভিড প্রশংসা করছে আমার। আমার ভদ্রতা হঠাৎ বেড়ে গেলো। মুখের হাসি আরো বিস্তৃত করে বললাম, “এসো এসো, ভেতরে এসো”।
রুমে ঢুকেই জোয়ানা বসে পড়লো আমার বিছানায়, আর ডেভিড হঠাৎ কিছু একটা মনে পড়ার ভঙ্গিতে বললো, “তুমি কিছু মনে না করলে একটা অনুরোধ করতাম তোমাকে”
আমার চোখ ডেভিডের মুখ ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে জোয়ানার পায়ের দিকে। আমার বিছানাটির উচ্চতা সম্ভবত স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি। নইলে জোয়ানার পা দুটো ফ্লোরে না লেগে এরকম দুলছে কীভাবে। স্কার্ট নামক যে বস্তুটা সে পরে আছে তা উঠে গেছে হাঁটুর উপরে।
“আমরা পিৎজার অর্ডার দিয়েছিলাম। কিন্তু এখন আমাদের কাছে ক্যাশ নেই। ডেলিভারিম্যান কার্ড নিচ্ছে না। তোমার কাছে যদি ক্যাশ থাকে তাহলে লোকটাকে দিতে পারি। সে দাঁড়িয়ে আছে বাইরে”
ডেভিডের উদ্দেশ্য বোঝা যাচ্ছে। তার কথা বিশ্বাস করবো কি করবো না ভাবার আগেই জোয়ানার দিকে চোখ গেলো আবার। সে ইতোমধ্যে বিছানায় এলিয়ে পড়ে পা নাচাতে নাচাতে বলছে, “প্রাডিবের বিছানাটা ডেভিডের বিছানার চেয়ে অনেক বেশি আরাম”
তেল দেবার কত রকমের আর্ট জানে মানুষ। কিন্তু তেল দিচ্ছে জানার পরেও যারা তৈলাক্ত হয় তাদের তুমি কী বলবে? যেমন সেই মুহূর্তের আমি?
বললাম, “কত লাগবে?”
“বিশ ডলার”
ওয়ালেট খুলে বিশ ডলারের একমাত্র নোটটা তুলে দিলাম ডেভিডের হাতে।
“এক ঘন্টার মধ্যেই আমরা এ-টি-এম থেকে ডলার তুলে ফেরত দেবো তোমাকে”
“না, না, পরে দিলেও চলবে। এই ঠান্ডায় আবার বাইরে যাবার দরকার কী?”
আমার নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছিলো না যে আমি এরকম দাতা কর্ণের মত বাণী দিচ্ছি।
“থ্যাংক ইউ প্রাডিব। ইউ আর গ্রেট। সি ইউ টুমরো” বলে বেরিয়ে গেলো ডেভিড আর জোয়ানা। আমি ওয়ালেটটা নিয়ে বসে রইলাম কিছুক্ষণ। লন্ডনের ছাপমারা সুন্দর ওয়ালেটটা পিয়া আমাকে দিয়েছে। তার আব্বু এনেছিলেন লন্ডন থেকে। ওটাতে এখন পাঁচ ডলারের একটা নোট আছে। স্কলারশিপের প্রথম কিস্তি গতকাল মানে শুক্রবার জমা হবার কথা ছিল। যদি না হয় খবর আছে আমার।
আজ সকাল সাড়ে সাতটার দিকে একবার উঠতে চেষ্টা করেছিলাম। কম্বলের ভেতর থেকে মাথাটা বের করতেই মনে হলো ডিপ-ফ্রিজের দরজা খুললাম। কোন মানে হয় না এত ঠান্ডায় এত সকালে ওঠার। ছুটির দিনের শীতের সকালের আলাদা একটা মর্যাদা আছে। যত দেরি করে বিছানা ছাড়া যায় ততই মর্যাদা বাড়ে। ঘুমের দ্বিতীয় পর্ব শুরু করলাম ঠিকই, কিন্তু ঘুম এলো না। এলো সব এলোমেলো চিন্তা। বাড়িতে মাঘ মাসের শীতের তাপমাত্রা কখনো নয়-দশ ডিগ্রির নিচে নামেনি। তাতেই মনে হতো- জমে যাবো ঠান্ডায়। অথচ এখানে এখন চার ডিগ্রির সকাল।
অস্ট্রেলিয়ায় আসার আগে উত্তর গোলার্ধ আর দক্ষিণ গোলার্ধের জলবায়ুর পার্থক্য নিয়ে কখনো ভেবেও দেখিনি। অথচ দেখো স্কুলের ভূগোল বইতে এসব আমাকে পড়তে হয়েছিল। মুখস্ত করে পরীক্ষার খাতার লিখেওছিলাম। তখন কি জানতাম নাকি ওই জ্ঞান কখনো কাজে লাগবে?
বেরোলাম দশটার পরে। লাইগন স্ট্রিট ধরে হাঁটতে হাঁটতে রয়েল এক্সিবিশান সেন্টার হয়ে পার্কের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পার্লামেন্ট স্ট্রিটে এসে সোজা ভিক্টোরিয়ার পার্লামেন্টের সামনে। ভিক্টোরিয়া রাজ্যটির আয়তন দুই লাখ সাতাশ হাজার ছয়শ’ বর্গ কিলোমিটার। বাংলাদেশের প্রায় দ্বিগুণ। অথচ এ রাজ্যের মোট জনসংখ্যা মাত্র পয়ঁত্রিশ লাখ। একেবারে রাস্তার সাথে লাগানো পার্লামেন্ট হাউজের সিঁড়ি। কোন রকম নিরাপত্তা ব্যবস্থাও আছে বলে মনে হলো না। মাত্র দু’জন পুলিশকে দেখলাম। তাদের একজন আবার একদল ট্যুরিস্টের ছবি তুলে দিচ্ছেন।
হাঁটতে হাঁটতে ট্রেজারি বিল্ডিং ছাড়িয়ে ফিট্জরয় গার্ডেন বামে রেখে ফ্লিন্ডার স্টিটে পৌঁছে গেলাম। সামনেই ইয়ারা। দক্ষিণ তীরে মেলা বসেছে- সানডে মার্কেট। ঘুরতে ঘুরতে জিনিস দেখলাম, মানুষ দেখলাম, নদী দেখলাম। তারপর পেটে টান পড়তেই চলে এসেছি। বিগ-ম্যাক খাবো কি না ভেবেছিলাম একবার। কিন্তু ডেভিড যদি বিশ ডলার ফেরত না দেয়, স্কলারশিপের টাকা যদি এ সপ্তাহেও জমা না হয়, তবে মাত্র পাঁচ ডলারে চলতে হবে।
ফেরার পথে সোয়ান্সটন স্ট্রিট। মানুষ দেখতে দেখতে ফেরা। ঘোড়ার গাড়ির ভীড় আর দুর্গন্ধ আজকেও আছে। ঠান্ডা হাওয়ার সাথে মেঘ-মাখা কিছু রোদও আছে। বার্ক স্ট্রিটের ফুটপাত-শিল্পীদের ছবি আঁকা আছে, ডেভিড-জোন্স আর মায়ারের সামনে আদিবাসীদের নাচ-গান আছে, সারা গায়ে রঙ মেখে যন্ত্রসাজা মানুষ আছে, ট্রাম আছে, বাস আছে, সারি সারি গাড়ি আছে, হাসি আছে, হুল্লোড় আছে। রোববারের মেলবোর্নে যা যা থাকার সবই আছে- অথচ মনে হচ্ছে কিছু একটা নেই- তীব্রভাবে নেই।
ক্রমশঃ______________

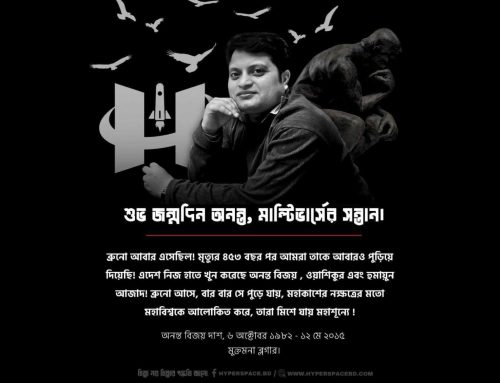
আসলেই দুর্দান্ত প্রদীপের লেখা। মুগ্ধতা নিয়ে সিরিজটি পড়ছি।
অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাস আসলেই এভাবে জানতাম না। পড়ে ভাল লাগলো। যদিও কলম্বাস, ক্যাপ্টেন কুকদের সম্বন্ধে আমার ধারণা খুব একটা উঁচু নয়। তারপরেও অস্ট্রেলিয়ায় বীর বলে কথা!
আমি ভেবেছিয়াম ডেভিডের উদ্দেশ্য প্রদীপকে গর থেকে বের করে দিয়ে কিছু সময়ে জন্য রুমের দখল নেয়া 🙂 । পিৎসার উপর দিয়েই গেছে দেখে আস্বস্ত(আসলে হতাশ) হলাম।
@অভিজিৎ,
আমিও তাই ভেবেছিলাম। বাংলাদেশে তো তাই ঘটে। রাজশাহীতে কলেজে পড়ার সময় কলেজ থেকে ফিরে প্রায়ই দেখতাম রুমের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। আমার রুমমেট এইচ এস সি শেষ করে ইন্ডিয়াতে পড়তে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন 🙂
মুগ্ধ হয়ে পড়ছি। তারপর? :rose:
অষ্ট্রেলিয়ার ইতিহাস এভাবে জানতাম না। শুধু জানতাম যে ক্যাপ্টেন কুকই
অষ্ট্রেলিয়ার আবিষ্কারক।
উইলিয়াম ড্যাম্পিয়ারকে জলদস্যু হিসেবে একটি বইতে পেয়েছিলাম, অবশ্য বলা ছিল প্রকৃতি প্রেমিক জলদস্যু।