লেখাটি আসিফের অনুরোধে বেশ কয়েক বছর আগে মহাবৃত্ত পত্রিকাটির জন্য লিখেছিলাম। তারপর আর মহাবৃত্ত বেরুনোর কোন নাম গন্ধ নেই। ভেবেছিলাম মহাবৃত্ত সহ পুরো লেখাটি বোধ হয় ব্ল্যাক হোলের গহবরে হারিয়ে গেল। কিন্তু মহাবৃত্ত হারায়নি। যেন, ফিনিক্স পাখির মত ছাই ভস্ম থেকে হাজির হয়েছে স্বমহিমায়। মহাবৃত্ত নিয়ে যখন আলোচনা চলছেই, তখন ভাবলাম এই সুযোগে আইনস্টাইন নিয়ে লেখাটা মুক্তমনায় দেয়া যায়। লেখাটি আগে মুক্তমনায় প্রকাশিত হয়নি।
আমার নিজের লেখা নিয়ে নিজের কোন আবেগ নেই। খুব একটা উঁচু ধারণাও যে আছে তাও বলা যাবে না। তারপরেও আমার হাজারো লেখার ছাই পাশের ভীরে এই লেখাটির আলাদা একটা স্থান আছে আমার কাছে। আমার খুব প্রিয় লেখাগুলোর একটি এটি। হয়তো পাঠকদেরও ভাল লাগবে। অধ্যাপক এ.এম হারুন অর রশিদ, অধ্যাপক অজয় রায়, ড.আলী অসগর, মফিদুল হক, আহসান হাবীব, মুনির হাসান সহ বহু বিখ্যাতজনের লেখার পাশাপাশি এ লেখাটিও মহাবৃত্তে স্থান করে নেয়ায় গৌরব বোধ করছি। আসিফকে ধন্যবাদ।
:line:
১
১৯৩০ সালের অক্টোবর মাসের এক মায়াবী শরৎ-সন্ধ্যা। লন্ডনের বিখ্যাত স্যাভয় হোটেলের বলরুমে চলছে পানাহারের হুল্লোর। ব্যারন রোথস্চাইল্ডের আথিতিয়তায় আয়োজিত এ দাতব্য অনুষ্ঠানে স্পটলাইট মূলতঃ দুই জীবন্ত কিংবদন্তীর উপর। এর একজন হচ্ছেন জর্জ বার্নার্ড শ, ১৯২৫ সালের নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক – শেক্সপিয়রের পরে যাকে ব্রিটেনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাট্যকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শ অবশ্য ‘সম্মানিত অথিতি’র স্পট লাইট নিজের উপরে নিতে রাজী নন; বললেন, সম্মানিত অথিতি যদি এ সভায় কেউ থেকে থাকেন তো সেটি ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী র্যামসে ম্যাক্ডোনাল্ড। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল মন্ত্রী সাহেব সে সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন নি। যথারীতি ক্যারিশমা দেখানোর ভারটুকু ঘুরে ফিরে বার্নাড শ’র উপরেই পড়ল। শ অবশ্য হতাশ করেননি। তার জীবনের অন্যতম ছোট্ট কিন্তু আকর্ষণীয় বক্তৃতায় শ সেদিন বললেন,
‘টলেমী’, শুরু করলেন শ, ‘এমন একখানা বিশ্বজগৎ আমাদের জন্য তৈরী করেছিলেন যা দুই হাজার বছর টিকে ছিল। তার পর নিউটন আরেকখানা জগৎ বানালেন যা তিনশ বছর টিকতে পেরেছিলো, আর আইনস্টাইন সম্প্রতি একটি বিশ্বজগৎ বানিয়েছেন, আমার ধারণা আপনারা চাইছেন আমি বলি এটি কখনই ফুরোবে না; কিন্তু আমি সত্যি সত্যিই জানি না কতদিন এ আইনস্টাইনীয় জগৎ টিকবে।’
দর্শকের সারিতে আইনস্টাইনও ছিলেন, আর শ’র কথা শুনে দর্শকদের সাথে সাথে তিনিও হো হো করে হেসে উঠলেন। শ এর বাকচাতুর্য আর রঙ্গরস এমনিতেই জগদ্বিখ্যাত ছিলো। সেদিনকার সভায় যেন ওটি আরো নতুন মাত্রা পেল। পদার্থবিজ্ঞানে আইনস্টাইনের অবদানকে তুলে ধরতে গিয়ে শ আইনস্টাইনের জীবনের নানা মজার মজার কাহিনী টেনে এনে তার বক্তৃতা শেষ করলেন এ বলে যে, ‘আইনস্টাইন হচ্ছেন আমাদের সমসাময়িকদের মধ্যে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠতম প্রতিভা’।
আইনস্টাইনও তো এ দিক দিয়ে কম যান না। বক্তৃতা দিতে উঠে শ কে মৃদু তিরষ্কার করলেন ‘আইনস্টাইন নামের অতীন্দ্রিয় মিথ্টির’ ভুয়ষী প্রশংসা করবার জন্য- যার কারণে নাকি তার জীবন ইতিমধ্যেই ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে! তার মতে, মানুষ তার সম্পর্কে যা কল্পণা করে আর বাস্তবে উনে নিজে যা – এর মধ্যে নাকি বিস্তর ফারাক!
তবে আইনস্টাইন নিজে তখন যাই বলুন না কেন, এখন কিন্তু প্রমাণিত হয়েই গেছে যে, শ’র কথা মোটেও অত্যুক্তি ছিলো না। আইনস্টাইনের যুগান্তকারী আবিস্কারের প্রায় একশ বছর এর মধ্যে পার হয়ে গেছে – এখনও আমরা সেই আইনস্টাইনীয় বিশ্বেই বাস করছি। ভবিষ্যতের কোন প্রতিভাধর বিজ্ঞানী যে বঙ্গমঞ্চে এসে আইনস্টাইনের এই বিশ্বজগতকে হটিয়ে দিতে পারবেন না, তা দিব্যি দিয়ে বলা যায় না, তবে এটুকু অন্ততঃ বলা যায় যে, আইনস্টাইন স্বীয় প্রতিভায় উদ্ভাসিত হয়ে নিজে এমন একটি জায়গায় পৌঁছে গেছেন, আর সেই সাথে আমাদের জ্ঞানকে নিয়ে গেছেন যে, তাকে পৃথিবীর সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভা হিসেবে মনে রাখতেই হবে- তা তার তৈরী বিশ্বজগৎ শেষ পর্যন্ত টিকুক আর নাই টিকুক।
২
তবে ‘জিনিয়াস’ বলতে যা বোঝায় তা কিন্তু ছেলেবেলায় কখনই ছিলেন না তিনি। বরং ‘মর্নিং শোজ দ্য ডে’- এ প্রবাদ বাক্যটি আইনস্টাইনের জীবনে নিদারুণভাবে ব্যর্থই বলতে হবে। ক্লাসের সেরা ছাত্র ছিলেন না আইনস্টাইন। বরং স্কুল কলেজের রেকর্ড যদি বিবেচনা করা হয়, নিতান্তই মাঝারি গোছের তার সমস্ত রেকর্ড। আইনস্টাইন এমনিতেই ছিলেন একটু ঢিলেঢালা; এমনকি শৈশবে কথা বলাও শিখেছিলেন একটু দেরী করে। দু বছরের বেশী লেগে গিয়েছিল। সাত বছর পর্যন্ত বাড়ীতেই পড়াশুনা চলে তার। এক সময় স্কুলেও ভর্তি করা হয় তাকে-ক্যাথোলিক স্কুলে। তবে ভর্তি করাই সার হল; স্কুলের পড়াশোনায় মোটেও মনোযোগী ছিলেন না আইনস্টাইন। একা একা ঘুরতেন, আপন মনে কি যেন ভাবতেন। স্বাভাবিকভাবেই রেজাল্ট আহামরি গোছের কিছু হচ্ছিল না। তবে রেজাল্টের চেয়েও গুরুতর কিছু সমস্যা নিয়ে বাবা মা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। শিক্ষকেরা অভিযোগ করেছেন আইনস্টাইন অন্য ছেলেদের সাথে একেবারেই মেশে না, পড়া মুখস্ত বলতে পারে না, আর প্রশ্ন করলে অনেক্ষণ লেগে যায় জবাব দিতে। আবার প্রায়ই জবাব দেওয়ার আগে কী যেন বিড়বিড় করে। প্রথম দূটো লক্ষণ না হয় তাও মানা গেল, কিন্তু তৃতীয়টা? ওটির কারণ আর কিছুই নয়- বেতের বাড়ির ভয়। ছোট্ট আইনস্টাইন ভাবলেন, ভুল-ভাল্ উত্তর দিয়ে স্যারের হাতের বেতের বাড়ি খাওয়ার চেয়ে বরং সতর্ক থাকাই তো ভাল! কাজেই ক্লাসে সবার সামনে উত্তর দেওয়ার আগে স্বগতোক্তি করে নিজের কাছেই উত্তরটা পরিস্কার করে নেওয়া- এই আরকি!
ছেলেবেলায় বন্ধুবান্ধবদের সাথে মিশতে না পারলে কি হবে- একটা কিন্তু খুব ভাল গুণ ছিলো তার। ওই যে চিরন্তন একগুয়ে স্বভাব। কোন একটা ব্যাপার মাথায় ঢুকে গেলে সেটার শেষ পর্যন্ত না দেখে তিনি ছাড়তেন না। এর নিদর্শন আমরা পাই আইনস্টাইনের ছোট বোন মাজা উইন্টারের লেখা ‘আলবার্ট আইনস্টাইন – আ বায়োগ্রাফিকাল স্কেচ’ গ্রন্থে। মাজা আইনস্টাইন সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেন -‘কোন কিছুতে একবার আকৃষ্ট হলে যেন রোখ চেপে বসত আইনস্টাইনের মাথায়। একবার বাড়িতে এসেছিলো মাজার কিছু খেলার সঙ্গী। সবাই মিলে মেতে উঠল তাসের ঘর বানানোর খেলায়। চারতলার চেয়ে বেশী আর কেউই বানাতে পারছিলো না। ঠিক এ সময় খেলায় যোগ দেন আইনস্টাইন। প্রথম প্রথম চেষ্টা করতে গিয়ে বেশ কয়েকবারই ভেঙে পড়ে তার তাসের ঘর। ব্যাস রোখ চেপে গেল আইনস্টাইনের। শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে করে যে ঘরটি বানালেন আইনস্টাইন – তা ছিলো চোদ্দ তলার!’
কিন্তু চোদ্দতলার তাসের ঘর বানানো এক কথা, আর পড়াশুনায় ভাল হওয়া আরেক। আইনস্টাইনের রিপোর্টকার্ডের ছিড়ি দেখে বাবা বাধ্য হলেন হেডমাস্টারের সাথে দেখা করতে। বাবা হেডমাস্টারকে জিজ্ঞাসা করলেন, বুঝলাম না হয় আলবার্ট পড়ালেখায় খারাপ করছে, কিন্তু এর মধ্যেও কি কোন পছন্দের বিষয় আছে, যা আলবার্টকে আকর্ষণ করে? মানে কোন বিশেষ সাব্জেক্টে সে কি আগ্রহ টাগ্রহ দেখায়? ভবিষ্যতে তার আগ্রহের বিষয় নিয়ে পড়ালেখা করলে যদি কোন ধরণের উন্নতি হয় – চিন্তাক্লিষ্ট বাবার মাথায় তখন হরেক রকম চিন্তা! হেডমাস্টার মশাই আলবার্টের বাবার এ ধরণের আশাবাদে যার পর নাই বিরক্ত হলেন। সরাসরিই বলে দিলেন, দেখুন বাপু, আপনার ছেলে একটু হাবলু টাইপ। ওকে নিয়ে এত আশাবাদী হয়ে লাভ নেই। মনে হয় না জীবনে কোন কিছুতেই সফল হবে আপনার ছেলে! কালের কি নির্মম পরিহাস- সেই ‘হাবলু টাইপ’ আইনস্টাইনকেই আজ কিন্তু মানুষ মনে রেখেছে, আর কালস্রোতে হারিয়ে গেছে ওই অর্বাচীন ‘জ্ঞানী’ হেডমাস্টার।
দশ বছর বয়সে আলবার্টকে ভর্তি করা হয় মিউনিখ শহরের লুটপোল্ড জিমনাসিয়াম স্কুলে। এখানেও ক্লাসের গৎবাঁধা পড়াশুনা তার জীবনকে নিরানন্দ করে তুল্লো। বিশেষতঃ গ্রীক ভাষা শেখার ক্লাসটি তো আইনস্টাইনের জন্য এক ‘মুর্তিমান বিভীষিকা’। ভাষার ব্যাকারণগুলো কিছুতেই মাথায় ঢুকতে চায় না তার। কাজেই ব্যকবেঞ্চার হয়ে হাসি হাসি মুখ করে শূন্যদৃষ্টিতে স্যারের দিকে তাকিয়ে থাকাই সার হল। মাস্টারমশাই হের যোসেফ ডেগেনহার্ট একই ঘটনা প্রতিদিন দেখতে দেখতে একসময় মহাবিরক্ত বোধ করলেন। সরাসরি বলে দিলেন এর পর থেকে আইনস্টাইন যেন আর ক্লাসে না আসে। কিন্তু এভাবে তো কাউকে ক্লাসে আসতে মানা করা যায় না, বিশেষতঃ আইনস্টাইন যখন ক্লাসে কোন দুষ্টুমী করেননি, কারো সাথে গোলমাল বাধাননি। তা হলে? বিরক্ত মাস্টারমশাই জবাব দিলেন, ‘হ্যা তা ঠিক। কিন্ত ওরকম হাবার মত হাসি হাসি মুখ করে ক্লাসে বসে থাকলে শিক্ষকমশাই যে সন্মানটুকু শ্রেণীকক্ষে একটি ছাত্রের কাছ থেকে আশা করেন, তা ক্ষুন্ন হয়।’
বোঝাই যাচ্ছে স্কুল জীবনটা ছিলো আইনস্টাইনের জন্য বিভীষিকাময় পীড়নকেন্দ্রের মত। স্কুলের ওই ভয়ার্ত অভিজ্ঞতার ছাপ আইনস্টাইনের পরবর্তী জীবনে সবসময়ের জন্যই বোধ হয় থেকে গিয়েছিলো। বুড়ো বয়সে এক সাক্ষাৎকারে আইনস্টাইন তাই বলেছিলন, ‘আমার কাছে প্রাথমিক স্কুলের স্যারদের মনে হত যেন মিলিটারী সার্জেন্ট, আর জিমনাসিয়াম স্কুলের শিক্ষকদের মনে হত যেন লেফটেনেন্ট’। এধরনের কথা কিন্তু বলেছিলেন বার্নার্ড শ ও। স্কুল জীবন সম্বন্ধে প্রায় একই ধরণের তিক্ত অভিজ্ঞতা হয় এই ব্রিটিশ সাহিত্যিকের। শ তার একটি লেখায় বলেন – ‘স্কুল জেলখানার চেয়েও বেশি নিষ্ঠুর জায়গা। জেলখানায় অন্ততঃ কয়েদীদের বাধ্য করা হয় না ওয়ার্ডেনদের লেখা বই পড়তে, অথবা বেত মারা হয় না শুকনো পাঠ্যবই মুখস্ত না বলতে পারলে’। শৈশবের স্কুল জীবনের বিভীষিকাময় পরিবেশের বাইরে সে সময় আইনস্টাইনের জীবনে সম্ভবতঃ একটিমাত্র আনন্দের বিষয় ছিল, তা হল তার চাচা জ্যাকবের সাহচর্য। তার এই চাচাই শৈশবে আইনস্টাইনকে পরিচয় করিয়ে দেন অংকের প্রধানতম শাখা বীজগনিতের সাথে অনেকটা এভাবে – ‘আলবার্ট, বীজগিত হচ্ছে মজার এক বিজ্ঞান, বুঝলে? মনে কর যে পশুটিকে শিকারের জন্য খুঁজছি কিন্তু তখনো ধরতে পারিনি, সেটার নাম নাম আমরা সাময়িকভাবে দেই X, আর যতক্ষণ না ওটাকে ধরতে পারি, আমরা খোঁজ চালিয়ে যেতে থাকি।’

জেকব চাচা ছাড়াও আরো ক’জনের প্রভাব আইনস্টাইনের উপর পড়েছিল। এর মধ্যে একজন হলেন ম্যাক্স ট্যাল্মি নামের এক গরীব মেডিকেলের ছাত্র, যে ছিল আইনস্টাইনদের বাসার ডিনারের ‘নিয়মিত অথিতি’। আসলে সে সময় দক্ষিণ জার্মানীর ইহুদীদের মধ্যে এক ধরণের রীতি প্রচলিত ছিল : প্রতি বৃহষ্পতিবার বাসায় কোন গরীব ইহুদীকে দাওয়াত করে খাওয়ানো। সে সূত্রেই ম্যাক্স ট্যাল্মির আইনস্টাইনদের বাসায় আসা। ফলাফল অবশ্য মন্দ হয়নি, এর কাছ থেকেই কিশোর আইনস্টাইন জ্যামিতি আর ক্যালকুলাস শেখার প্রাথমিক অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন।

আর ছিলেন আইনস্টাইনের মা। তবে তিনি জ্যামিতি বা ক্যালকুলাস শেখায় কোন সাহায্য করেন নি, করেছিলেন বেহালা শিখায়। এই বেহালা এবং সর্বপোরি সংগীত প্রীতি আইনস্টাইনের শেষ দিন পর্যন্ত বহাল ছিলো। তার জীবনীকার ডেনিস ব্রায়ান ‘আইনস্টাইন – আ লাইফ’ (১৯৯৬) গ্রন্থে আইনস্টাইনের সঙ্গীতপ্রিয়তার একটি ঘটনা উল্লেখ করেন এভাবে – ‘একবার আইনস্টাইন তার মধ্যবয়সে যথারীতি হেলতে দুলতে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। হাতে ছিলো তার প্রিয় বেহালাখানা। হঠাৎ শুনলেন রাস্তার ওপারের এক বাসা থেকে পিয়ানোর আওয়াজ ভেসে আসছে। আইনস্টাইন দৌড়ে বাসার কাছে চলে আসতে আসতে মহিলাকে বললেন- থেমো না, থেমো না, বাজাতে থাক! বলতে বলতেই বাক্স থেকে নিজের বেহালাটি বের করে ফেললেন, আর মহিলার সাথে তালে তাল মিলিয়ে বাজাতে লাগলেন। আইনস্টাইনের এ ধরণের স্বতঃস্ফুর্ততা ছিলো সত্যই বিস্ময়কর।’ আইনস্টাইনের সঙ্গীতপ্রিয়তার আরেকটি বড় একটি উদাহরণ আমরা পরবর্তীতে পাই রবীন্দ্রনাথের সাথে সাক্ষাৎকারের সময় (১৯৩০)। রবীন্দ্রনাথ জার্মানীতে আইনস্টাইনের বাসায় বেড়াতে এলে তারা দু’জনেই প্রাচ্য আর প্রতীচ্যের সঙ্গীত নিয়ে গভীর আলোচনায় নিমগ্ন হয়েছিলেন। সাক্ষাৎকারটির অনুলিখন যিনিই পড়েছেন, তিনিই বুঝেছেন যে, পদার্থবিজ্ঞানের কাঠখোট্টা জগতের বাইরেও তার ছিলো সঙ্গীতপ্রিয় সরস এক শিল্পী মন।
তবে আসল উপকারটি যিনি করেছিলেন তিনি তার জ্যাকব চাচাও নন, ম্যাক্স ট্যাল্মিও নন, এমনকি তার মা ও হয়ত নন, উপকারটি করেছিলেন তার বাবা – সেই ছোট্টবেলায় আইনস্টাইনকে একটি সামান্য কম্পাস কিনে দিয়ে। আইনস্টাইনের বয়স তখন কতই বা হবে – চার/পাঁচ! কম্পাসের কাঁটা যে সবসময় উত্তর-দক্ষিণে মুখ করে থাকে- এ ব্যাপারটা আইনস্টাইনকে যার পর নাই বিস্মিত করেছিল। ছোট্ট আইনস্টাইন ঘুমানোর সময়ও শুয়ে শুয়ে ভাবতো যে, কম্পাসের কাঁটা কেন শুধু উত্তর-দক্ষিণে মুখ করে থাকবে! নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে এর পেছনে। মাঝরাতে বাবা এসে দেখেন আইনস্টাইন তখনো ঘুমায়নি। বাবাকে দেখেই আইনস্টাইনের প্রশ্ন – ‘আচ্ছা বাবা, কম্পাসের কাঁটা কেন কেবলই এক দিকে মুখ করে থাকে?’ বাবা গম্ভীর গলায় বললেন – ‘ম্যাগনেটিজম্’। তারপরই বলতেন ‘আলবার্ট, অনেক রাত হয়েছে, এখন ঘুমানোর চেষ্টা কর তো।’ ঘুমিয়ে যেতে যেতেই আইনস্টাইন ভাবতেন, হুমম্ ম্যাগনেটিজম – বড় হয়ে ব্যাপারটা আরো ভাল করে বুঝতে হবে।
৩
তা আইনস্টাইন বড় হয়ে ভালই বুঝেছিলেন। বুঝেছিলেন বলেই তিনি ‘বড় হয়ে’ আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিজম বা তড়িচ্চুম্বকীয় মূল নীতির সংস্কার সাধন করে, যার ভিত্তি গড়ে উঠেছিলো আইনস্টাইন-পূর্ব বিজ্ঞানী- মুলতঃ নিউটন, ফ্যারাডে, কুলম্ব, গ্যালভানি, অ্যাম্পিয়ার, ম্যাক্সয়েল, হেলমোলজের ক্রমিক অবদানে।
সঙ্গতঃ কারণেই ১৯০৫ সালটিকে আইনস্টাইনের জীবনের ‘বিস্ময় বছর’ বলা হয়, করণ ও বছরটিতেই আইনস্টাইন মৌলিক আবিস্কারগুলো করেছিলেন। তার আগ পর্যন্ত আইনস্টাইনের পরিচিতি ছিল অনেকটা যেন ‘অ্যামেচার পদার্থবিদ’ হিসেবে। জুরিখের পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ভর্তি পরীক্ষায় তো এক্কেবারে ফেলই করে বসলেন। পরে অবশ্য তার সাধের এই পলিটেকনিকে একটু অন্যভাবে ভর্তি হতে পেরেছিলেন (ভর্তি পরীক্ষায় আর দ্বিতীয়বার না বসেই)। ভর্তি হলে কি হবে, ফলাফল কিন্তু যেই কি সেই।
ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষায় বসেন চারজন ছাত্র ও একজন ছাত্রী। প্রথম হন লুই কলরস (স্কোর ৬০), দ্বিতীয় মার্সেল গ্রসম্যান (স্কোর ৫৭.৫), জ্যাকব এহরাট (৫৬.৫), এর পর আইনস্টাইন (৫৪), শেষ স্থান মিলেভা মারিকের (৪৪, ফেল্) যিনি পরবর্তীতে আইনস্টাইনের স্ত্রী হন। তার মানে ফেলের হাত থেকে বাঁচলেও পাশ করা ছাত্রদের মধ্যে আইনস্টাইনের স্থান হয় সবার শেষে। রেজাল্ট খারাপই কেবল একমাত্র বিষয় নয়, এর মধ্যে পদার্থবিজ্ঞানের বিভাগীয় প্রধানকেও দিলেন চটিয়ে। প্রফেসর ওয়বার নামের অধ্যাপক মশাইটি চাইতেন ছাত্ররা তাকে সব সময় ‘হের প্রফেসর’ বলে ডাকুক (আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা যেমন সারাদিনই স্যার স্যার করা পছন্দ করেন, অনেকটা ওরকম আরকি!)। আইনস্টাইন ব্যাপারটি বুঝলেও তাকে স‘হের ওয়েবার’ নামে সম্বোধন করে যেতেন। এর ফলে প্রফেসর সাহেব এমনই খ্যাপা খেপেন যে, পরীক্ষার আগে তিনি আইনস্টাইনকে একটি স্টাডি পেপার দু’দুবার লিখতে বাধ্য করেন।

সে যাই হোক, পরীক্ষার লবডংকা ফলাফলের খেসারত ভালই দিলেন আইনস্টাইন। সহপাঠীদের মধ্যে চাকরী হল না কেবল তারই। নানা কলেজে দরখাস্ত করলেন তিনি, কিন্তু কোথা থেকেও কোন উত্তর এলো না। নিজ প্রতিষ্ঠানেও কোন আশার আলো দেখতে পেলেন না আইনস্টাইন।
সেই ওয়েবার মশাই যিনি এমনিতেই আইনস্টাইনের উপর খাপ্পা ছিলেন, তিনি ঘোষনা করে দিলেন যে এবছর তিনি কোন পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র তার অধীনে কাজ করার জন্য নেবেন না, নেবেন একজন পুরোদস্তুর মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়র। বোঝাই যায়, পাছে আইনস্টাইন আবেদন করে বসেন এই ভয়েই তড়িঘড়ি অমন ঘোষণা দিয়েছিলেন তিনি। যা হোক, বেকার আইনস্টাইনকে শেষ পর্যন্ত সাহায্য করেছিলেন তার পলিটেকনিকের সহপাঠী গ্রসম্যান।
তার বাবাকে অনুরোধ করে কোন রকমে আইনস্টাইনের জন্য গ্রসম্যান একটা চাকরী জুটিয়ে দিলেন সুইস পেটেন্ট অফিসে। পদ – প্রবেশনারি টেকনিকাল এক্সপার্ট, থার্ড ক্লাস। হ্যা – ওখানেই চাকরী শুরু করলেন আইনস্টাইন, ধীরে ধীরে সহকর্মীদের শ্রদ্ধাভাজনও হতে শুরু করলেন, কিন্তু এর বেশী কিছু আইনস্টাইনকে দেখে তখন বোঝা যায়নি। কিন্তু মাস খানেকের মধ্যেই পরিস্থিতি গেল বদলে। ওই ‘অজ্ঞাতকুলশীল’ সাধারণ পেটেন্ট ক্লার্কের চিন্তার ঝড়ে আক্ষরিকভাবেই লন্ডভন্ড হয়ে গেল পৃথিবী। এমনই লংকাকান্ড বেধে গেল যে, পদার্থবিদদের এতদিনকার চীরচেনা বিশ্বজগতের ছবিটাই গেল আমূল বদলে। পুরোপদার্থবিজ্ঞানের চীরচেনা জগৎটাকেই ঢেলে সাজাতে হল, পাঠ্যপুস্তকগুলোও লিখতে হল এক্কেবারে নতুন করে! তা পেটেন্ট অফিসে বসে কি করলেন আইনস্টাইন? তাঁর ওই ‘বিস্ময় বছরের’ প্রথমভাগে প্রকাশ করলেন ব্রাউনীয় গতির উপর একটা পেপার- যেটি আমাদের দিল পরমানুর অস্তিত্বের বাস্তব প্রমাণ, বানালেন আলোর কনিকা বা কোয়ান্টাম তত্ত্ব, আর প্রকাশ করলেন সবচাইতে জনপ্রিয় আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বটি। তার বিখ্যাত সমীকরণ =E=mc2 বাজারে আসল একটি অতিরিক্ত (সংযোজনী) তিন পৃষ্ঠার পেপার হিসেবে। একটি পেপারের জন্য আবার পরবর্তীতে পেলেন নোবেল। আইনস্টাইন আর ‘আ্যামেচার পদার্থবিদ’ রইলেন না, থাকলেন না পৃথিবীবাসীর কাছে ‘অজ্ঞাত’ হিসেবে। ১৯১৯ সালে আইনস্টাইনের তত্ত্বের ব্যবহারিক প্রমাণ মিলল, তখন আইনস্টাইন রীতিমত তারকা। সে বছর নিউইয়র্ক টাইমস ব্যানার হেডলাইন করে ফিচার করল –
‘Einstein Theory Triumphs’।
Times of London লিখল,
‘Revolution in Science … Newtonian Ideas overthrown’।
আইনস্টাইনের আসন সে দিন থেকে পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে রীতিমত স্থায়ী হয়ে গেল। তার জীবনীকার দেনিস ব্রায়ান Einstein: A Life গ্রন্থে লিখেছেন,
‘He was regarded by many as an almost supernatural being, his name symbolizing then – as it does now- the highest reaches of the human mind’।
সত্যই তাই। ‘আইনস্টাইন’ শব্দটি উচ্চারণ করলেই মনে যে হিমালয়-সম তুংগস্পর্শী মানব প্রতিভার অবয়ব চোখের সামনে ভেসে ওঠে তার ভিত্তি রচিত হয়েছিল সে সময়ই। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের রুজ বল প্রফেসর রজার পেনরোজের মতে,
‘আমাদের পরম সুবিধা এই যে, এই বিংশ শতাব্দীতে আমরা দু-দুটো বিপ্লবের সাক্ষী হয়েছি। প্রথমটিকে আমরা বলি আপেক্ষিকতা, আর দ্বিতীয়টি চিহি¡ত হয়েছে কোয়ান্টাম তত্ত্ব নামে। অবাক ব্যাপার যে – একজন মাত্র বিজ্ঞানী – আলবার্ট আইনস্টাইন – তার অসাধারণ মনন আর অনুসন্ধিৎসা বলে ১৯০৫ সালে মাত্র এক বছরের ভিতর রচনা করেছিলেন ওই দু-দুটো বিপ্লবেরই।’
৪
আপেক্ষিকতার তত্ত্ব উদ্ভাবনের পেছনে রয়েছে আইনস্টাইনের অসাধারণ কিছু মানস পরীক্ষা (Thought Experiment)* । ‘অসাধারণ’ শব্দটি লিখলাম বটে, কিন্তু বর্ণনা শুনলে মনে হবে এ তো খুবই সাধারণ। এতোই সাধারণ, যে কারো মাথায়ই হয়ত আসবে না যে, এগুলো কোন চিন্তার বিষয় হতে পারে। আইনস্টাইনের অসাধারণত্ব ওখানেই। সাধারণ আর হাল্কা বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে করতে অসাধারণ সমস্ত জটিল সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারতেন। সেই সতের বছর বয়সে হঠাৎ করেই একদিন আইনস্টাইনের মাথায় এসেছিলো একটি অদ্ভুতুরে প্রশ্ন : ‘আচ্ছা, আমি যদি একটা আয়না নিয়ে আলোর গতিতে সা সা করে ছুটতে থাকি, তবে কি আয়নায় আমার কোন ছায়া পড়বে?’

ছবিঃ আমি যদি একটা আয়না নিয়ে আলোর গতিতে সা সা করে ছুটতে থাকি, তবে কি আয়নায় আমার কোন ছায়া পড়বে?
প্রশ্নটা শুনতে সাধারণ মনে হলেও এর আবেদন কিন্তু সুদূরপ্রসারী। এই প্রশ্নটি সমাধানের মধ্যেই আসলে লুকিয়ে ছিল আপেক্ষিকতার বিশেষতত্ত্ব (Special Theory of Relativity) সমাধানের বীজ। আলোর গতিতে চললে আয়নায় কি ছায়া পড়ার কথা? আমাদের প্রাত্যহিক যে অভিজ্ঞতা, তার নিরিখে বলতে গেলে বলতে হয় পড়বে না। কেন?
কারণটা সোজা। গ্যালিলিও-নিউটনেরা বস্তুর মধ্যকার আপেক্ষিক গতির যে নিয়মকানুন শিখিয়ে দিয়েছিলেন, তা থেকে বুঝতে পারি আলোর সমান সমান বেগে পাল্লা দিয়ে চলতে থাকলে আইনস্টাইনের সাপেক্ষে আলোকে তো এক্কেবারে গতিহীন মনে হবার কথা। ফলে আলোর তো আইনস্টাইনকে ডিঙ্গিয়ে আয়নায় ঠিকরে পড়ে আবার আইনস্টাইনের চোখে পড়বার কথা নয়। তাহলে ওই পরিস্থিতিতে আইনস্টাইন কিন্তু নিজের ছায়া আয়নায় দেখতে পাবেন না। আরো সোজাসুজি বললে বলা যায়, আয়না মুখের সামনে ধরে যদি আলোর বেগের সমান বেগে দৌড়ুতে থাকেন, তবে আইনস্টাইন দেখবেন যে আয়না থেকে আইনস্টানের প্রতিবিম্ব রীতিমত ‘ভ্যানিশ’ হয়ে গেছে। কিন্তু তাই যদি হয় এই ব্যাপারটা জন্ম দিবে আরেক সমস্যার। এতোদিন ধরে গ্যালিলিও যে ‘প্রিন্সিপাল অব রিলেটিভিটি’ নামের সার্বজনীন এক নিয়ম আমাদের শিখিয়েছিলেন, সেটা তো আর কাজ করবে না। গ্যালিলিওর এই আপেক্ষিকতার নিয়মটা আগে একটু একটু বোঝার চেষ্টা করা যাক। এই যে আমরা পৃথিবী নামের গ্রহের কাঁধে সওয়ার হয়ে সূর্যের চারিদিকে সেকেন্ডে ১৬ মাইল বেগে অবিরাম ঘুরে চলেছি, তা আমরা কখনো টের পাই না কেন? কারণ আমাদের অবস্থান তো পৃথিবীর বাইরে নয়। পৃথিবী আমাদেরকে সাথে নিয়েই প্রতিনিয়ত লাট্টুর মত ঘুরে চলেছে। কাজেই আমাদের সাপেক্ষে পৃথিবীর আপেক্ষিক গতি তো সবসময়ই স্রেফ শূন্যই থাকে। সেজন্যই আমরা পৃথিবীর গতিকে কখনো উপলব্ধি করি না। ঠিক একই ধরনের অভিজ্ঞতা হয় আমাদের যখন আমরা স্টিমারে, লঞ্চে কিংবা জাহাজে করে নদী কিংবা সমুদ্র পাড়ি দেই। অনেক সময় আমরা ডেকের ভিতরে থেকে বুঝতেই পারি না লঞ্চ বা জাহাজটা চলছে কিনা। কেবল মাত্র বাইরের দিকে তাকিয়ে যখন দেখি তীরের গাছপালা বাড়িঘরগুলো সব পেছনের দিকে চলে যাচ্ছে, তখনই কেবল বুঝি যে আমাদের জাহাজটা আসলে সামনের দিকে এগুচ্ছে। পৃথিবীর ঘূর্ণনের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। কেবল আকাশের দিকে তাকিয়ে আমরা যখন সূয্যি মামাকে পূব থেকে পশ্চিমে চলে যেতে দেখি, তখনই আমরা কেবল বুঝি যে আমাদের পৃথিবীটা হয়ত আমাদেরকে সাথে নিয়ে পশ্চিম থেকে পূবে পাক খেয়ে চলেছে। এই বিভ্রান্তিটাই কিন্তু গ্যালিলিওর ‘প্রিন্সিপাল অব রিলেটিভিটি’র মূলকথা। গ্যালিলিও বলেছিলেন যে, কেউ যদি সমবেগে ভ্রমণ করতে থাকে (ধরুণ জাহাজে করে) তবে তার (জাহাজের ডেকের ভিতরে বসে) কোন ভাবেই বুঝবার বা বলবার উপায় নেই যে সে এগুচ্ছে, পিছাচ্ছে নাকি স্থির হয়ে দাড়িয়ে আছে। কিন্তু তাই যদি হয়, তবে জাহাজটি যদি আলোর বেগে চলে তবে তো এই সার্বজনীন ব্যাপারটি খাটবে না। জাহাজের ডেকে বসে স্রেফ আয়নার দিকে তাকিয়েই কিন্তু জাহাজযাত্রীবুঝে যাবেন যে তার জাহাজটি চলছে, কারণ তিনি তার প্রতিবিম্বকে আয়না থেকে ‘ভ্যানিশ’ হয়ে যেতে দেখবেন।
তাহলে? তাহলে আর কিছুই নয় – আইনস্টাইন বুঝলেন, হয় গ্যালিলিওর প্রিন্সিপাল অব রিলেটিভিটি ভুল, আর নয়ত আইনস্টাইনের মানসপরীক্ষার মধ্যেই কোথাও গলদ রয়ে গেছে। অবশ্যই সতেরো বছর বয়সে এই ধাঁধার কোন সমাধান পাননি আইনস্টাইন, কিন্তু এ নিয়ে অনবরত চিন্তা করেই গেছেন।
সমাধান পেয়েছেন শেষ পর্যন্ত সুইস পেটেন্ট অফিসে চাকরী শুরু করার মাস খানেকের মধ্যে। আইনস্টাইন বুঝলেন যে, গ্যালিলিওর প্রিন্সিপাল অব রিলেটিভিটির মধ্যে কোন ভুল নেই। আয়না থেকে ছায়া ভ্যানিশ হওয়া ঠেকাতে হলে আলোর গতির ব্যাপারটিকে একটু ভিন্নরকম ভাবে ভাবতে হবে; আর দশটা সাধারণ বস্তু কণার বেগের মত করে ভাবলে চলবে না। আইনস্টাইন বললেন, ‘আলোর বেগ তার উৎস বা পর্যবেক্ষকের গতির উপর কখনই নির্ভর করে না; এটি সব সময়ই ধ্রুবক।’ ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত। মন মানতে চায় না; কারণ এই ব্যাপারটি বস্তুর বেগ সংক্রান্ত আমাদের সাধারণ পর্যবেক্ষণের একেবারেই বিরোধী। যেমন ধরা যাক, আপনি একটি রাস্তায় ৪০ কি.মি বেগে গাড়ী চালাচ্ছেন। আপনার বন্ধু ঠিক বিপরীত দিক থেকে আরেকটি গাড়ী নিয়ে ৪০ কি.মি বেগে আপনার দিকে ধেয়ে এল। আপনার কাছে কিন্তু মনে হবে আপনার বন্ধু আপনার দিকে ছুটে আসছে দ্বিগুন (৪০ + ৪০ = ৮০ কি.মি) বেগে। আলোর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্যরকম। ধরা যাক, একজন পর্যবেক্ষক সেকেন্ডে ১ লক্ষ ৫০ হাজার কিলোমিটার বেগে আলোর উৎসের দিকে ছুটে চলেছে। আর উৎস থেকে আলো ছড়াচ্ছে তার নিজস্ব বেগে – অর্থাৎ সেকেন্ডে প্রায় ৩ লক্ষ কিলোমিটারে। এখন কথা হচ্ছে পর্যবেক্ষকের কাছে আলোর বেগ কত বলে মনে হওয়া উচিৎ? আগের উদাহরণ থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতা বলে – সেকেন্ডে (১ লক্ষ ৫০ হাজার + ৩ লক্ষ =) ৪ লক্ষ ৫০ হাজার কিলোমিটার। আসলে কিন্তু তা হবে না। পর্যবেক্ষক আলোকে সেকেন্ডে ৩ লক্ষ কিলোমিটার বেগেই তার দিকে আসতে দেখবে। ব্যাপারটা ব্যতিক্রমী সন্দেহ নেই, কিন্তু এ ব্যাপারটা না মানলে গ্যালিলিওর ‘প্রিন্সিপাল অব রিলেটিভিটি’র কোন অর্থ থাকে না। আইনস্টাইন তার তত্ত্বের সাহায্যে আরো দেখালেন, যদি কোন বস্তু কণার বেগ বাড়তে বাড়তে আলোর গতিবেগের কাছাকাছি চলে আসে, বস্তুটির ভর বেড়ে যাবে (mass increase) নাটকীয় ভাবে, দৈর্ঘ্য সঙ্কুচিত হয়ে যাবে (length contraction) এবং সময় ধীরে চলবে (time dialation)। সময়ের ব্যাপারটা সত্যই অদ্ভুত। বিজ্ঞানী-অবিজ্ঞানী বির্বিশেষে সবাই সময় ব্যাপারটিকে এতদিন একটা ‘পরম’ (absolute) কোন ধারণা হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন; সময় ব্যাপারটা রাম-শ্যাম-যদু-মধু সবার জন্যই ছিলো সমান, যেন মহাবিশ্বের কোথাও লুকিয়ে থাকা একটি পরম ঘড়ি অবিরাম মহাজাগতিক হৃৎস্পন্দনের তালে তালে স্পন্দিত হয়ে চলছে, টিক্, টিক্, টিক্, টিক্… … যার সাথে তুলনা করে পার্থিব ঘড়িগুলোর সময় নির্ধারণ করা হয়। কাজেই সময়ের ব্যাপারটা আক্ষরিক আর্থেই ছিল পরম, কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর কোনভাবেই নির্ভরশীল নয়। কিন্তু আইনস্টাইন রঙ্গমঞ্চে হাজির হয়ে বললেন, সময় ব্যাপারটা কোন ভাবেই ‘পরম’ নয়, বরং আপেক্ষিক। আর সময়ের দৈর্ঘ্য মাপার আইনস্টাইনীয় স্কেলটা লোহার নয়, যেন রাবারের – ইচ্ছে করলেই টেনে লম্বা কিংবা খাটো করে ফেলা যায়! রামের কাছে সময়ের যে দৈর্ঘ্য তা রহিমের কাছে সমান মনে নাও হতে পারে। বিশেষতঃ রাম যদি দ্রুতগতিতে চলতে থাকে, রহিমের তুলনায় রামের ঘড়ি কিন্তু আস্তে চলবে! আরেকটা জিনিস বেরিয়ে আসল আইনস্টাইনের তত্ত্ব থেকে। শূন্য পথে আলোর যা গতিবেগ, কোন বস্তুর গতিবেগ যদি তার সমান বা বেশী হয়, তবে সমীকরণগুলো নিরর্থক হয়ে পড়ে। এ থেকে একটা সিদ্ধান্ত করা হয়েছে – কোন পদার্থই আলোর সমান গতিবেগ অর্জন করতে পারবে না। সেই থেকে মহাবিশ্বের গতির সীমা নির্ধারিত হয় আলোর বেগ দিয়ে।
আইনস্টাইন আপেক্ষিকতার এই বিশেষ তত্ত্ব দিয়েই কিন্তু ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারতেন। ১৯০৫ সালে তার গবেষণাপত্রটি জার্নালে প্রকাশের পর থেকেই পদার্থবিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, সুইস পেটেন্ট অফিসের এক অখ্যাত কেরানী অচীরেই পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা করতে যাচ্ছেন। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার জনক ম্যাক্স প্লাঙ্ক তখনই উচ্চকিত হয়ে উঠেছিলেন এই বলে : ‘যদি (আপেক্ষিক তত্ত্ব) সত্য বলে প্রমাণিত হয়, তবে আইনস্টাইন বিংশশতাব্দীর কোপার্নিকাস হিসেবে বিবেচিত হবেন।’
কিন্তু আইনস্টাইন কেবল বিশেষ তত্ত্ব নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে বসে থাকার মানুষ নন। আবিষ্কারের নেশা তখন যেন তাকে পেয়ে বসেছে। তিনি মন দিলেন আরো উচ্চাভিলাসী গবেষণায়। এর ফলাফল হিসেবেই ক’বছরের মধ্যে উঠে আসলো সার্বিক অপেক্ষিক তত্ত্ব (General Theory of Relativity)। এই গবেষণা মানে আর গুণে এমনই অনন্য যে, আইনস্টাইন নিজেই একসময় উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই গবেষণার কাছে তার আগের আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব তো স্রেফ ‘ছেলে খেলা’। মজার ব্যাপার হচ্ছে আইনস্টাইনের এই সার্বিক অপেক্ষিক তত্ত্বের পেছনেও কিন্তু রয়েছে আরেকটি সার্থক মানস পরীক্ষা। হঠাৎ একদিন আইনস্টাইনের মাথায় আসলো একটা লোক উঁচু একটা বাড়ীর ছাদের উপর থেকে পড়ে গেলে কি হবে? কি আবার হবে! ধপ্পাস করে মাটিতে-তারপর দুম ফট! আমাদের মত ছা-পোষা মানুষেরা তো বটেই, অধিকাংশ বিজ্ঞানীরাই ওভাবে চিন্তা করতেন। কিন্তু আইনস্টাইন ওভাবে ভাবলেন না। সাধারণ একটা ঘটনার মধ্যেও অসাধারণত্বের ছোঁয়া খুঁজে পেলেন। তিনি দুর্ভাগ্যবান মানুষটির মাটিতে ভুপাতিত হবার ঠিক আগের মুহূর্তটির ‘সৌভাগ্যের’ কথা ভাবলেন, যেটিকে তিনি আখ্যায়িত করেছেন ‘হ্যাপিয়েস্ট থট অব মাই লাইফ’।

কি পেলেন আইনস্টাইন ওই পতনশীল মানুষটির মাটিতে আঘাত করার আগ-মুহূর্তের মধ্যে? পেলেন এই যে, ওই পতনশীল মানুষটি নিজের ওজন অনুভব করবে না। আইনস্টানের কাছে এ ব্যাপারটির মানে দাঁড়ালো, মহাকর্ষ ক্ষেত্রের মধ্যে মুক্তপতনশীলতার অভিজ্ঞতা আর মহাকর্ষবিহীন শূন্যাবস্থায় ভেসে থাকার মধ্যে আসলে কোন পার্থক্য নেই। সেখান থেকেই তিনি বের করে আনলেন ‘ইকুইভ্যালেন্ট প্রিন্সিপাল’- যা হয়ে দাঁড়ালো সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্বের মূল ভিত্তি।
আইনস্টাইন পরবর্তীতে তার ঐতিহাসিক তত্ত্বের সাহায্যে মহাকর্ষের সাথে আপেক্ষিকতাকে সন্নিবদ্ধ করে দেখালেন যে, মহাকর্ষকে শুধু শুন্যস্থানে দুটি বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ বল (নিউটন যেভাবে চিন্তা করেছিলেন) হিসেবে ভাবলে চলবে না, ভাবতে হবে আপাতঃ শক্তি (aparent force)হিসেবে যার উদ্ভব হয় আসলে মহাশূন্যের (space) নিজস্ব বক্রতার কারণে। তার এ তত্ত্ব থেকেই আমরা বুঝতে পেরেছি, কোন আকর্ষণ বল-টল নয় বরং বিশাল ভরের কারণে মহাশুন্যে সৃষ্টি হয় বক্রতা যা কোন বস্তুকণার গতিপথকে – এমনকি আলোর গতিপথকেও বাঁকিয়ে দেয়। আমাদের সৌরজগতের কেন্দ্রে সূর্য থাকার কারণেও কিন্তু সৃষ্টি হয়েছে বক্রতা যার কারণে পৃথিবী সহ অন্যান্য গ্রহগুলোকে একটি বক্রতলে সূর্যের চারদিকে ঘুরতে দেখা যায়। প্রফেসর আর্কিবালড হুইলারের ভাষায় -‘পদার্থ স্পেসকে বলছে কিভাবে বাঁকতে হবে, আর স্পেস পদার্থকে বলছে কিভাবে চলতে হবে’! এটাই আসলে নিউটনের মহাকর্ষকে আইনস্টাইনের চোখ দিয়ে দেখা।
৫
কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা নিয়েও আইনস্টাইন বিভিন্ন ধরনের মানস পরীক্ষা করেছিলেন তার জীবনের শেষ তিন দশকে। অনেকগুলোই তৈরী করেছিলেন কোয়ান্টাম বলবিদ্যা বিষয়ে বিখ্যাত ডেনিস বিজ্ঞানী নীলস্ বোরের সাথে তর্কে লিপ্ত হয়ে। যদিও আইনস্টাইন ১৯০৫ সালে নোবেল পুরস্কারটিই পেয়েছিলেন কোয়ান্টাম বলবিদ্যার উপর- সেই যে ‘ফটো-ইলেকট্রিক ইফেক্ট’ যার মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছিলেন আলো আসলে কতকগুলো শক্তিকণার (কোয়ান্টা) সমষ্টি, কিন্তু এই আইনস্টাইনই আবার পরবর্তীতে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সম্ভাবতার জগতের সাথে একাত্মতা ঘোষনা করতে পারেন নি। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার অনিশ্চয়তাকে খন্ডন করতে গিয়ে তার ‘ঈশ্বর পাশা খেলেন না’ উক্তিটি তো সর্বজনবিদিত।
কোয়ান্টাম বলবিদ্যাকে অসম্পূর্ণ প্রমাণ করতে তিনি অনেকগুলো মানসপরীক্ষার ক্ষেত্র তৈরী করেন; এর মধ্যে বিখ্যাতটি হল ‘ই.পি.আর’ পরীক্ষণ, যেটি তিনি তৈরী করেন ন্যাথান রোজেন আর বরিস পোডলস্কির সাথে মিলে। ১৯৩৫ সালে তার সেই মানসপরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয় ফিজিকাল রিভিউ জার্ণালে Can Quantum Mechanical Description of Physical Reality Be considered Complete? শিরোনামে।
আইনস্টাইনের সবগুলো মানস পরীক্ষাই ছিলো খুবই সহজ সরল যা পদার্থবিজ্ঞানের একেবারে প্রাথমিক জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। আইনস্টাইনের কৃতিত্ব এখানেই যে তিনি ওই সব সহজ সরল সাধারণ বিষয়গুলোকে নিয়ে চিন্তা করতে করতে ধীরে ধীরে জটিল তত্ত্বে উপনীত হতেন। আবার অনেক সময় জটিল জিনিসকে নিয়ে আসতেন জনমানুষের সাধারণ বোধগম্যতার স্তরে। একবার বিজ্ঞানের এক ‘ক অক্ষর গোমাংস’ সাংবাদিক ‘আপেক্ষিকতার মূল বিষয়টি কি?’ জিজ্ঞাসা করলে, আইনস্টাইন উত্তরে বললেন,
‘আপনি চুলার আগুনে আপনার হাতটি এক মিনিটের জন্য ধরে রাখুন, সেই এক মিনিটকে মনে হবে এক ঘন্টা। কিন্তু এক সুন্দরী তরুনীর সাথে এক ঘন্টা ধরে কথা বলুন, সেই একঘন্টাকে মনে হবে এক মিনিট। এটাই আপেক্ষিকতা।’
আইনস্টাইনের আস্থা ছিলো পর্যবেক্ষণ অনপেক্ষ ভৌত বাস্তবতায়। তিনি বিশ্বাস করতেন না মানুষের পর্যবেক্ষণের উপর কখনও ভৌতবাস্তবতার সত্যতা নির্ভরশীল হতে পারে। বোর প্রদত্ত কোয়ান্টাম বলবিদ্যার কোপেনহেগেনীয় ব্যাখ্যার সাথে তার বিরোধ ছিল মূলতঃ এখানেই। বোর বলতেন, ‘পদার্থবিজ্ঞানে কাজ প্রকৃতি কেমন তা আবিষ্কার করা নয়, প্রকতি সম্পর্কে আমরা কি বলতে পারি আর কিভাবে বলতে পারি, এটা বের করাই বিজ্ঞানের কাজ।’ এই ধরণাকে পাকাপোক্ত করতে গিয়ে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার আরেক দিকপাল হাইজেনবার্গ দেখিয়েছিলেন যে, একটি কণার অবস্থান এবং বেগ যুগপৎ নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করা অসম্ভব।
অবস্থান সুচারুভাবে মাপতে গেলে কনাটির বেগের তথ্য হারিয়ে যাবে, আবার বেগ খুব সঠিকভাবে মাপতে গেলে অবস্থান নির্ণয়ে গন্ডগোল দেখা দেবে। নীলস বোরের মতে, যতক্ষণ পর্যন্ত না একটি কণাকে পর্যবেক্ষণের আওতায় আনা যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কণাটি কোথায় রয়েছে – এটা বলার কোন অর্থ হয় না। কারণ এটি বিরাজ করে সম্ভাবনার এক অস্পষ্ট বলয়ে। অর্থাৎ এই মত অনুযায়ী ভৌতবাস্তবতা মানব-পর্যবেক্ষণ নিরপেক্ষ নয় (১৯৮২ সালে অ্যালেইন অ্যাস্পেক্ট আইনস্টাইনের ই.পি.আর মানস পরীক্ষাকে পূর্ণতা দান করেন একটি ব্যবহারিক পরীক্ষার মাধ্যমে, যা বোরের যুক্তিকেই সমর্থন করে)। বলা বাহুল্য, আইনস্টাইন এ ধরনের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। একবার বোরের যুক্তিতে অনুপ্রাণিত এক বন্ধু তাকে রাস্তায় মানব পর্যবেক্ষণের সাথে কোয়ান্টামীয় ভৌত বাস্তবতার সম্পর্ক বোঝাতে চাইছিলেন। বিরক্ত আইনস্টাইন আকাশের দিকে আঙ্গুল তুলে বলে উঠলেন –
‘তুমি বলতে চাইছো, ওই যে চাঁদটা ওখানে আছে, আমরা না দেখলে চাঁদটার অস্তিত্ব থাকবে না?’
এই হচ্ছেন আইনস্টাইন। দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কিছু উপমা আর সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনার মাধ্যমে বিশ্বজগতের জটিল রহস্যের সমাধান করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। প্যাভিয়ার রাস্তায় হেটে বেড়ানো একসময়কার ‘ভাবুক’ বালক বড় হয়ে স্রেফ কতকগুলো মানস পরীক্ষার মাধ্যমে চীরচেনা জগতের ছবিটাই আমূল পাল্টে দিয়েছিলেন, আর জীবনের শেষ বছরগুলো নিস্ফলভাবে কাটিয়েছিলেন কোয়ান্টাম বলবিদ্যার ‘আজগুবী’ সিদ্ধান্তগুলোকে হটাতে; মানবিকতার সাধনায় আর প্রকৃতির মৌলিক বলগুলোকে একীভূত করবার উচ্চাভিলাসী স্বপ্ন নিয়ে হেঁটে গিয়েছিলেন অনেকদূর – একাকী, নিঃসঙ্গভাবে!
===================
* বিঃ দ্রঃ মানস পরীক্ষাগুলো (Thought Experiment) কোন বাস্তব পরীক্ষা নয়, বরং কল্পিত পরীক্ষা। পরীক্ষাগুলো ঘটে আসলে পদার্থবিদদের মাথার ভিতরে, কোন ল্যাবরেটরীতে নয়। মুলতঃ যন্ত্রপাতির সীমাবদ্ধতা এবং অন্যান্য কারণে এ ধরনের পরীক্ষাকে বাস্তবে রূপ না দেওয়া গেলেও পদার্থবিদদের মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাওয়া এ পরীক্ষাগুলোর গুরুত্ব কিন্তু অপরিসীম।

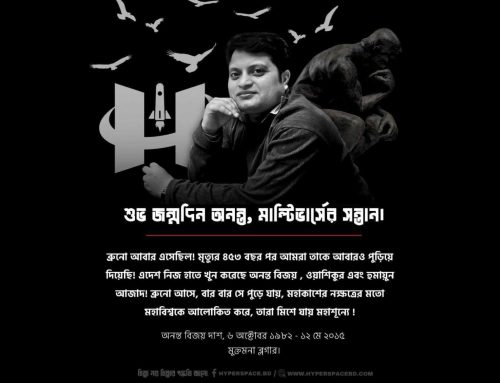
ভাবছিলাম আমি এই লেখাটার বানান ভুল নিয়ে কিছু লিখব কারণ এত অসাধারণ একটা লেখায় এ ধরণের ভুল দেখতে খারাপ লাগে। কিন্তু পথিক ভাইয়া কাজটা করে দিয়েছেন।এজন্য তাকে সাধুবাদ জানাই। লেখাটা দারুন। শেষের অংশে যেখানে তত্ত্বগুলো বর্ণনা করা হেয়েছে সে অংশটা মনে হচ্ছে ভালভাবে বুঝতে হলে আবার পড়তে হবে কারণ এখন মাথা ব্যাথা করছে তাই বেশি মনযোগ দিতে পারলামনা।
আচ্ছা মুক্তমনার কোন পোস্ট ভাল লাগলে সেটাকে নিজের প্রোফাইলে ‘প্রিয়’ বা ‘ফেভারিট’ করা যায় আমার ব্লগ এর মত? একটু জানাবেন প্লিজ। আর যদি এমন ব্যবস্থা না থাকে তাহলে চালু করা যায়না?
সত্যেন বোস ও অন্যান্য বাঙ্গালী বিজ্ঞানীদের নিয়ে কোন লেখা বইয়ের কথা জানা থাকলে নাম ও প্রকাশনীর নাম জানাবেন দয়া করে।
@প্রদীপ দেব,
আপনার আইনস্টাইনকে নিয়ে লেখা বইটা কোন প্রকাশনীর? জানালে কিনে পড়তাম। আর আপনার বাঙলী বিজ্ঞানীদের নিয়ে লেখা সিরিজটা বই হিসেবে প্রকাশিত হবে কবে ও কোন প্রকাশনী থেকে জানাবেন অনুগ্রহ করে।
খুব ভালো লাগলো লেখাটি। দেশে যাব কদিন বাদেই ‘মহাবৃত্ত’কে অবশ্যপাঠ্য তালিকায় যুক্ত করলাম।
@তানভীরুল ইসলাম,
ধন্যবাদ পাঠ প্রতিক্রিয়ার জন্য। মহাবৃত্তের জন্য আগ্রহ সৃষ্টি করায় সফল হওয়াতেও গৌরববোধ করছি।
অভিজিতের সবচেয়ে বড় গুণ হলো অনেক জটিল বিষয়কে তিনি বেশ সহজভাবে বুঝিয়ে দিতে পারেন। আমাদের সব শিক্ষক যদি অভিজিতের মত হতেন তাহলে বিজ্ঞানে আমাদের দুর্দশা কিছুটা কমতো। দারুণ ভালো লাগলো। প্রাণবন্ত আলোচনা থেকে বাংলা বানান সম্পর্কেও অনেক কিছু জানা গেলো। একটা ছোট্ট ব্যাপার এখানে উল্লেখ করছি – আইনস্টাইনের বোনের নাম মায়া (মাজা নয়)। জার্মান ‘j’ এর উচ্চারণ ‘য়’।
@প্রদীপ দেব,
অনেক ধন্যবাদ আইনস্টাইনের বোনের সঠিক জার্মান উচ্চারণটি জানানোর জন্য।
আপনি বাঙালি বিজ্ঞানীদের নিয়ে যে সিরিজটা শুরু করেছেন সেটা কি সামনে বই হিসেবে বেরুচ্ছে?
আইনস্টাইন শিখতে এসে বানান শিখলাম। শুদ্ধ বানান কি জরুরী?
@বিপ্লব পাল,
না ‘জরুরী’ নয় জরুরি। 🙂 (সূত্রঃ বাংলা একাডেমি আর আনন্দবাজার)
বাংলা নানানের প্রতি আপনার এই উদাসীনতা আমাকে ভীষণ অবাক করে। অথচ ইংরেজির ক্ষেত্রে অনেকেই আবার অতি সচেতন। ইংরেজি বানান ভুল করলে লজ্জার সীমা থাকে না অথচ বাংলার ক্ষেত্রে ওটা ‘জাস্ট আ মিসটেক। বাংলা ভাষার প্রতি লোক দেখানো দরদ না দেখিয়ে আমাদের সবারই ভাষাটা ভালভাবে শিখে নেওয়া দরকার। মুক্তমনায় আমি নতুন হলেও এখানে দেখেছি শুদ্ধ বানানের প্রতি সবসময় উৎসাহ দেওয়া হয়। অনেকেই মুক্তমনায় এসে নিজের ভুল গুলো শুধরে নিয়েছেন। যেমন ফুয়াদ ভাই এর প্রথমদিকে শুদ্ধ বাংলা ও ব্যাকরণে কিছুটা অসুবিধা থাকলেও ব্লগারদের উৎসাহে নিজেকে দ্রুত শুধরে নিয়ে রীতিমত ব্লগিং পর্যন্ত করছেন।প্রমিত বাংলা ভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে অচেতন হলে প্রমিত ইংরেজিতেই ব্লগিং শ্রেয়। নইলে আমার,অভিজিতদা,ব্লাডি সিভিলিয়ান আর ফরিদ ভাই এর ফরিয়াদ মাঠে মারা যাবে! 😀
আসলে আইনস্টাইন,রবীন্দ্রনাথ বা হরমুজ মিয়া- যে সম্পর্কেই হোক লেখাটায় বানান ভুল থাকলে সেটার আবেদন অনেকটাই নষ্ট হয়ে যায়। আর বেগার খাটা বানান-পুলিশদের উৎসাহ দেওয়ার বদলে শুদ্ধ বানানের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তোলাটা বেশ অদ্ভুত বটে! 🙁 :-X :-Y :-/ 😉
আইনস্টাইন কি শিখেননি? সাথে কয়েকটা শুদ্ধ বানান শিখলে দোষ কি??
@পথিক,
প্রিন্ট মিডিয়ার সময় সাধারণত যেভাবে কাজ হত-লেখকরা হাতে লিখতেন, প্রিন্টের আগে প্রফেশনার প্রুফ রিডাররা বানান চেক করে প্রকাশ করতেন। বাংলা ব্লগে সেটা হবার জো নেই। নিজেদের করতে গেলে, আবার অনেক সময় দিতে হবে। এখানে কেওই পেশাদার লেখক না-তবে অনেকেই যত্ন নিয়েই লেখেন। আমার ভাই অত সময় নেই। আমি যেভাবে বলছি, সেই ফ্লোতেই লিখি।
ইংরেজীতে লেখার সময় আজকাল যেকোন সফটওয়ার বানান ট্রাক করে-ফলে ভুল হলে সেটা বোঝা যায়। বাংলায় স্পেল চেকার নেই। বা এখনো আসে নি। ধরছি আর দুই এক বছরের মধ্যেই আসবে-তখন এসব সমস্যা হবে না।
লেখাটা অসাধারণ ভাল হয়েছে। পদার্থবিজ্ঞান বলতেই অনেকের শুধু রকেট,এল এইচ সি বা বড় বড় স্থাপনার কথা মনে পড়ে। কিন্তু বিজ্ঞানীর মনের অতুলনীয় ক্রিয়া-প্রক্রিয়া তথা ভাবনা-চিন্তার মাধ্যমে এ কত বড় বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়ে যায় সেটা এই মানস পরীক্ষার ঘটনা দিয়েই বুঝে নেওয়া যায়। আপেক্ষিকতা নিয়ে আরো কতগুলো সমস্যা আমার খুব ভাল লাগে। সময় সংকোচন,ট্রেন সমস্যা, যমজ সমস্যা আর গোয়ালঘরে আলোর দ্রুত খুঁটি প্রবেশের সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতে খুব ভাল লাগে। আসলে শাফায়েত ঠিকই বলেছে। সবাই মাওলানা বিবর্তনবাদী হয়ে গেলে আমার মত মূর্খদের তো বিরাট বিপদ! অভিদার কাছ থেকে কোয়ান্টাম মেকানিক্স নিয়ে ভাল কিছু লেখা চাই।
কিন্তু এই অসাধারণ লেখাটায় এত বানান ভুল আর ব্যাকরণগত সমস্যা আছে সেটা দ্রুত শুধরে নেওয়া উচিত। ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা করায় এখন বানান ও ব্যাকরণ দূর্বলতা বোধ করি। সাদা চোখে এই বানানগুলো ভুল মনে হচ্ছে।বাপুরা(বানান-পুলিশ)নিশ্চিত করলে ভাল হয়।
ছাই পাশের ভীরে>> ছাইপাশের ভীড়ে
হুল্লোর>> হুল্লোড়
আথিতিয়তায়>> আতিথিয়তায়
রাজী>>রাজি
সম্মানিত অথিতি>>অতিথি
ভুয়ষী>>ভূয়সী
কল্পণা করে আর বাস্তবে উনে নিজে যা>>কল্পনা,উনি
আবিস্কারের>>আবিষ্কারের
বঙ্গমঞ্চে>>রঙ্গমঞ্চে
দেরী>>দেরি
বেশী>>বেশি
পড়াশুনা>>>পড়া-শোনা
মুখস্ত>>মুখস্থ
শিক্ষকেরা>>শিক্ষকরা/শিক্ষকবৃন্দ
প্রথম দূটো>>প্রথম দুইটি
পরিস্কার>>পরিষ্কার
আরকি>> আর কি
ছিড়ি>>ছিরি
মুর্তিমান>>মূর্তিমান
ব্যাকারণগুলো>>ব্যাকরণ
ব্যকবেঞ্চার>>ব্যাকবেঞ্চার
দুষ্টুমী >>দুষ্টুমি
সন্মানটুকু>>সম্মানটুকু
ক্ষুন্ন >>ক্ষুণ্ণ
এক গরীব মেডিকেলের ছাত্র>মেডিকেলের এক গরীব ছাত্র অথবা এক গরীব মেডিকেল ছাত্র
নিয়মিত অথিতি>> নিয়মিত অতিথি
করেছিলেন বেহালা শিখায়>>শেখায়
সর্বপোরি >>সর্বোপরি
আইনস্টাইন-পূর্ব বিজ্ঞানী- মুলতঃ>> আইনস্টাইনপূর্ব বিজ্ঞানীগণ- মুলতঃ
চাকরী>>চাকরি
চীরচেনা>>চিরচেনা
পুরোপদার্থবিজ্ঞানের চীরচেনা>>পুরো পদার্থবিজ্ঞানের চিরচেনা
কনিকা>>কণিকা
হাল্কা>>হালকা
অদ্ভুতুরে>>অদ্ভুতুড়ে
ধরুণ>>ধরুন
জাহাজযাত্রীবুঝে>> জাহাজযাত্রী বুঝে
দ্বিগুন>>দ্বিগুণ
অচীরেই>>অচিরেই
দুর্ভাগ্যবান>>দুর্ভাগা
ভুপাতিত>>ভূপাতিত
তরুনীর>>তরুণীর
এছাড়া বিরাম চিহ্নতেও অনেক সমস্যা আছে। আইন্স্টাইন, বোর ,রবীন্দ্রনাথ সব ক্ষেত্রেই তার ও যার কে তাঁর ও যাঁর দ্বারা পুনঃস্থাপন করলে ভাল হয়। পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে সবার কাছ থেকে এই রকম আরো লেখা প্রত্যাশা করি।
@পথিক,
:yes:
এটা আমার একটা পুরানো লেখা ছিলো, নতুন করে পোস্ট দেয়ার সময় বানানগুলো দেখে নেয়া আসলেই উচিৎ ছিলো। কষ্ট করে এতগুলো বানান নজরে আনার জন্য ধন্যবাদ।
অসাধারণ একটা লেখা, মুক্তমনায় আমার পড়া সেরা লেখাগুলোর তালিকায় এটা একেবারে উপরে থাকবে। এর আগে লার্জ হ্ড্রেন কলাইডার নিয়ে কেশব অধিকারীর একটা লেখা খুব ভালো লেগেছিল। মুক্তমনায় এ ধরনের লেখা আরো বেশী দরকার। দুঃখজনক হলেও সত্য “বিবর্তন” বাদে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাথা নিয়ে লেখাগুলোতে হিট,কমেন্ট কম পড়ে, এগুলো নিয়ে তেমন কেও আলোচনা করতে চায়না অথচ বিবি আয়েশার পুরোনো কাহিনী নিয়ে লেখা আসলেই সে লেখা হিট হয়ে যায়। এভাবে বিজ্ঞানমনস্কতা কিভাবে তৈরী হবে? পাঠক-লেখকদের অনুরোধ করব বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা নিয়ে লিখতে, লিখতে না পারলে যারা লিখছেন তাদের উৎসাহ দিতে।
@রামগড়ুড়ের ছানা,
ধন্যবাদ রামগড়ুড়ের ছানা চমৎকার একটা মন্তব্যের জন্য।
আসলেই অন্য বিষয় নিয়েও ভাল লেখা দরকার। তোমারেই তো বললাম, প্রোগ্রামিং এর বেসিক নিয়ে মজাদার কিছু পোস্ট দাও, শুনলানা…
@অভিজিৎ,
প্রায় ১২ ঘন্টা আগে একটা মন্তব্য করার জন্য বোতাম টিপতেই মুক্ত-মনা বলল এই বিষয়ে মন্তব্য নেয়া বন্ধ হয়ে গেছে। জানতাম যন্ত্র কোথাও গণ্ডগোল করেছে, যাইহোক এখন আবার চেষ্টা করছি।
প্রথমতঃ আপনার প্রাঞ্জল লেখা পড়ে ভাল লাগল। আমি আপনাকে অনুরোধ করব আইনস্টাইন বা অন্য যে কোন বিজ্ঞানীর ওপর in-depth বইএর ব্যাপারে ভাবতে। ইংরেজী বা অন্যান্য ভাষায় অনেক ভাল বই আছে, কিন্তু আইনস্টাইনের ওপর বাংলায় কোন authoritative বই নেই। গ্রামে-গঞ্জে বিজ্ঞান পৌঁছানর জন্য বাংলার দরকার আছে। বাংলায় যে সমস্ত জীবনী বের হয় সেগুলো যেন কোন ডেডলাইনের পাল্লায় পড়ে প্রথম দশ-বারো পাতার পরে মুষড়ে পড়ে, তারপর তরিঘড়ি (বানান?) করে শেষ হয়ে যায়। আর যেহেতু সেখানে বই ছাপানোর আগে রেফারীগিরি হয় না, তথ্য ভুলে পুরো জিনিসটার শেষ পর্যন্ত কোন মূল্যই থাকে না। ভাল ভাষা, ভাল গবেষণা, তথ্যের যথার্থতা ও ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খতা একটা ভাল বিজ্ঞান জীবনীর জন্য অপরিহার্য। আপনি এটা চেষ্টা করে দেখতে পারেন।
@দীপেন ভট্টাচার্য,
প্রদীপ দেবের একটা বইআছে “আইনস্টাইনের কাল” নামে দেখতে পারেন আমার বেশ ভালই লেগেছে।
তবে অভিজিৎ দার কাছে দাবী সবসময়ই থাকবে আরো বেশীকরে লেখার জন্যে।
:-Y :-Y
ইহা দেশের ইন্টারনেটের দুরবস্থা আর অভিজিৎ রায়ের বেশ কিছু বানান ভুলের ফল!(যেগুলো তিনি এখনও ঠিক করেননি,মনে হয় ফরিদ দা এর হস্তক্ষেপ লাগবে :lotpot: )। যাইহোক ৪-৫ মিনিট এ অবস্থা ছিল,দুঃখিত।
শুনলাম না? জানেনইতো এখন পরীক্ষা। এরপর লেখার ইচ্ছা আছে। বিবর্তনবাদীদের(আপনাকে সহ) আইপিসহ ব্যান করে দিয়ে মুক্তমনাকে প্রোগ্রামিং ব্লগ বানানোর ইচ্ছা আমার অনেকদিন।
কিন্তু একটা ব্যাপারে ভয়ে আছি। আমি মাত্র প্রথম সেমিস্টারের ছাত্র,দেখা যাবে “বেসিক” নিয়ে লিখলাম আর বড় ভাইরা দাবড়ানি দিয়ে বলবে “ওই মিয়া, তোমার নিজেরইতো বেসিক ঠিক নাই!!”.
আপনাকে জরুরী মেইল করেছি, চেক করেন।
@রামগড়ুড়ের ছানা,
আমার বানান ভুলের কারণে ইন্টারনেটে ঢোকা যায় না, এটা কম্পিউটার প্রোগামারের কাছ থেকে শোনাটা বিরাট বিস্ময়! 🙂
আসল কথা হল, রামগড়ুড়ের ছানা সাহেব পথিকের দেয়া বানান ভুলের তালিকা দেখে আমার প্রতি করুণাবশতঃ লেখাটা ঠিক করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু ইন্টারনেটের স্পিডের কারণে লেখার অর্ধেকটা হাপিশ হয়ে যায়। তার পর থেকেই রামগড়ুড়ের ছানাের মাথা একটু আউলানো 😀
বাই দ্য ওয়ে রামগড়ুড়ের ছানা, আদিল মাহমুদ সাহেব ইমেইল করেছেন – উনার নাকি লগ ইন এ সমস্যা হচ্ছে। একটু দেখো তো …
@অভিজিৎ,
পথিক সাহেব আজকে দেখসেন, আর আমাকে একজন কাল রাতে দেখিয়েছে। আর জনতার আদালতই বলবে এটা কার দোষ। :-X
আপনাকে ৩টা অ্যাটাচমেন্ট সহ একটা মেইল পাঠিয়েছি গতকাল, ওটার উত্তর দিচ্ছেননা কেন? :guli:
আদিল চাচার পাসওয়ার্ড বদলে দিয়েছি, এখন লগইন করা যাচ্ছে।
[email protected] এই আইডিতে নতুন লগইন পাঠিয়ে দিচ্ছি। উনি এটাই ব্যবহার করেনতো??
@দীপেন ভট্টাচার্য,
আমি আইনস্টাইন সম্বন্ধে যা জানি সবই পপুলার লেভেলে। ‘ইনডেপথ’ কিছু লিখতে হলে আপনি কিংবা প্রদীপ দেবের মত পদার্থবিজ্ঞানীদেরই দায়িত্ব নিতে হবে। প্রদীপ দেবের অবশ্য আইনস্টাইনকে নিয়ে চমৎকার একটা বই আছে ‘আইনস্টাইনের কাল’ নামে। বইটির অনলাইনের কপি আপনি প্রদীপ দেবের আর্টিকেল পেইজে পাবেন (পেইজের একদম নীচের দিকে আছে সিরিজটা)। প্রদীপ অবশ্য বাঙ্গালী বিজ্ঞানীদের নিয়েও চমৎকার একটা সিরিজ শুরু করেছেন সম্প্রতি। ওটাও একদিন বই হয়ে উঠবে নিশ্চয়।
আর তো বাকি আছেন আপনি। আপনার লেখার গুণ মান এতোই ভাল যে এটা নিয়ে আলাদা করে কিছু বলবার নেই। তার উপর পদার্থবিজ্ঞান আপনার নিজের বিষয়। কাজেই লিখলে আপনাকেই লিখতে হবে আইনস্টাইনের উপর authoritative বই।
@অভিজিৎ,
নিদ্রালু ও আপনাকে ধন্যবাদ। দোষটা আমারই। আইনস্টাইনের ওপর প্রদীপ দেবের লেখার সিরিজটা ও বইটার কথা জানা ছিল না, শীতস্তম্ভে ছিলাম! ওনার সঙ্গে ইদানিং কালে মুক্তমনার বদৌলতেই যোগাযোগ হয়েছে। বাঙ্গালী বিজ্ঞানীদের নিয়ে ওনার লেখাগুলি আগ্রহ সহকারে পড়ছি। লিঙ্কটা দেবার জন্য ধন্যবাদ।
আমার ওপর বিশ্বাস স্থাপন হচ্ছে অপাত্রে দান। ব্রাইসন যদি ইংরেজীর লোক হয়ে সব বিজ্ঞানীকে টেক্কা দিতে পারে, আপনার মত পরীক্ষিত লেখক (ও বিজ্ঞানী) এই কাজটা অনায়াসে করতে পারে।
যেটাই হোক – মুক্তমনার মাধ্যমে অনেক কিছু হচ্ছে ও ব্যক্তিগতভাবে অনেক কিছু শিখছি।
@রামগড়ুড়ের ছানা, ইশশশ… বিবর্তনবাদ আর আয়েশাকে এক করে দিলেন? আতঙ্কজনক ব্যপার :-Y । কি আর করবেন, এই দেখেন না, শিক্ষানবিস,রায়হান, অভিজিতরাই তো একসময় অন্যান্য বিষয়গুলো নিয়ে লিখতো, এখন তারাও তো দেখি বিবর্তন ছাড়া আজকাল আর কিছু নিয়ে লিখালিখি করেনা, আপনার উচিত এই লেখকদের ফাঁসি দাবী করা :laugh:।
@রামগড়ুড়ের ছানা,
ভাইয়া লিংকটা একটু দিবেন? আমি খুজে পাচ্ছিনা। কেউ জানলে প্লিজ একটু শেয়ার করুন।
@মিঠুন,
কি করব বলেন, বিবর্তনের কারনে অন্য বিজ্ঞানের টপিক একটু বেশী চাপা পড়ে যাচ্ছে। তবে বিবর্তনের গুরুত্ব অস্বীকার কখনোই করছিনা।
অভিজিৎ দা খাল কেটে কুমির এনেছেন, এখন দাবী করবনা, সোজা ব্যান করে দিব :rotfl: :rotfl: ।
আপনাকে কয়বার করে বলেছি আমাকে ‘তুমি’ করে বলতে? :guli: :guli:
অভি, কাহিনী এখন আর কাহিনী নেই, ‘বিবর্তনের পথ ধরে’ তা কাহিনি হয়ে গেছে। 🙂
@ফরিদ আহমেদ,
বানানের এরকম বিবর্তন হলে আর যারই হোক ব্লাডি সিভিলিয়ানের মনে ধরবে না এইটা হলফ করেই বলা যায়। আপনার আর্টিকেলে দাবরানি খাইছেন, আবার উনারে এইখানেও টাইনা আইনেন না। ব্যাকরণ আর বানান বিশারদদের আমি খুবই ভয় পাই। 🙂
@অভিজিৎ,
ব্লাডি সিভিলিয়ানরে আমার ডাইকা আনোন লাগবো না। তোমারই দেখতাছি তার দাবড়ানি খাওনের শখ জাগছে। কইতাছি যে কাহিনী বানান বদলায়া গ্যাছে গা, বিশ্বাস করতাছো না। খাও দাবড়ানি, আমার কী? 🙂
@ফরিদ আহমেদ,
কাহিনি শব্দটা বিদেশি, এর বিবর্তন অপ্রত্যাশিত নয়, কিন্তু আমাদের চির চেনা শব্দের বিবর্তনে কিছুটা বিভ্রান্ত হই।
প্রবন্ধটিতে বেশ কিছু যায়গায় দীর্ঘ ইকার আর হ্রস্ব ইকার এর বিবর্তিত রূপ ব্লাডিসিভিলিয়ানের চোখকে ফাঁকি দিল কী ভাবে সেটাই আশ্চর্য।
অভিজিৎ দা,
কী আর করা দাদা, অপরাধ হলে ক্ষমা করবেন। বিজ্ঞানের জটিল বিষয়াদি নিয়ে না বুঝে মন্তব্য করার চেয়ে এই পথেই প্রবন্ধে কমেন্টের সংখ্যা বাড়ানোর ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা করলাম।
রামগড়ুড়ের ছানা,
সময়ের প্রয়োজনে আয়েশাদের প্রবন্ধে হিট, কমেন্টের সংখ্যা বেশি ছিল, হয়তো আরো কিছু দিন থাকবে। তবে সেদিন বেশি দূরে নয়, বিবর্তনের পথ ধরে আবার, সময়ই আয়েশাদের প্রবন্ধের উপর বিজ্ঞানের প্রাধান্য এনে দিবে। একদিন আয়েশাদের নিয়ে প্রবন্ধ লেখার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে, কেউ আর তা লিখবেনা। ততদিন পর্যন্ত আমাদেরকে আরজ আলী মাতুব্বরের পথ ধরে চলতে হবে। একদিকে ধর্মকে বিজ্ঞানের কাঠগড়ায় , অন্যদিকে ধর্মগ্রন্থ থেকেই ইসরাফিলের শিঙ্গা ও কিরামান কাতিবিন ফেরেস্তাকে টেনে বের করে এনে যুক্তি ও বিবেবেকের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন।
@অভিজিৎ,
‘কাহিনী’ শব্দটা বহুল প্রচলিত এবং শুদ্ধ বলেই মান্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের নাম রেখেছেন ‘কথা ও কাহিনী’।
আমিও তাই লিখতাম। একটা ব্যাপারে শব্দটার উৎস খুঁজতে গিয়ে নিচের তথ্যগুলো আবিষ্কার করলাম।
‘চলন্তিকা’ (রাজশেখর বসু) এবং ‘সংসদ বাঙ্গালা অভিধান’ (শৈলেশ বিশ্বাস)-এ পেলাম শব্দটা সংস্কৃত ভাষা থেকে নয়, হিন্দি ‘কহানি’ থেকে আগত। তাই, অবশ্যই ‘কাহিনি’, কারণ বিদেশি শব্দে দীর্ঘ-ঈ বর্জিত।
আবার ‘বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান’ জানাচ্ছে শব্দটা সংস্কৃত ‘কথনিকা’ থেকে এসেছে। তাই, অর্ধ-তৎসম হিসেবে এতেও হ্রস্ব-ই-ই হবে।
অতএব, এই হৈল কাহিনি।
তবে,….
ব্যাকরণের একটা বিখ্যাত নিয়ম হচ্ছে, সবাই মিলে একটাই ভুল করতে থাকলে সেটা আর ভুল নয়, শুদ্ধ বলেই গণ্য হয়।
এদিক থেকে এটারে একটা বেনিফিট অব সন্দেহ দিচ্চেন কেউ কেউ; আপাতত আমি তাঁদের সাতে নেই। 😛 😛 😛
@ব্লাডি সিভিলিয়ান,
কাহিনী বানানটা বহুল প্রচলিত তাতে কোন সন্দেহ নেই, তবে একে শুদ্ধ বলে মান্য করা হয় না মোটেও। বাংলা একাডেমীর বানান অভিধানে কাহিনির অন্য কোন বিকল্প বানান দেওয়া হয়নি।
বাংলা ভাষাটাকে যারা খুব ভাল জানতেন তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই অন্যতম। তবে, এর মানে এই না যে তিনি বানান ভুল করতেন না। বা তিনি ভুল বানান লিখলেই সেটি শুদ্ধ হয়ে যাবে। অনেক শব্দ বা শব্দের বানান নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমসাময়িক ভাষাবিদরের অনেক চ্যালেঞ্জের মুখেই পড়েছেন। সেগুলোর কিছু কিছুকে তিনি মেনে নিয়েছেন, কিছু কিছুকে মেনে নেননি। এর স্বপক্ষে তাঁর নিজের যুক্তি পেশ করেছেন। বাংলা বানানের শৃঙ্খলহীনতা দেখেই একে শাসন করার জন্য তাঁর উদযোগেই কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সংস্কার কমিটি গঠন করে। যার সুফল এখন আমরা পাচ্ছি। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথের সময়ে যে বানানটাকে শুদ্ধ বলে মনে করা হতো পরবর্তীতে বিভিন্ন বানান সংশোধন কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে হয়তো তার অনেক কিছু এখন ভুল বলে গণ্য করা হচ্ছে। কাজেই, রবীন্দ্রনাথ লিখেছে বলে সেই দোহাই দিয়ে ভুল বানানকে শুদ্ধ বলার সুযোগ নেই বোধহয়।
সংস্কৃত শব্দ নয় বরং কাহিনির মূল উৎস নিহিত রয়েছে প্রাকৃততে। যদিও হিন্দি কহানী, সিন্ধি কিহাণী বা মারাঠী এবং গুজরাটি কহাণীর সাথে এর মিল রয়েছে। কিন্তু আমার ধারণা শব্দটা মূলত এসেছে প্রাচীন মৈথিলি ভাষার শব্দ কহিনী থেকে। প্রাচীন মৈথিলি ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি বিদ্যাপতি লিখেছেন, “কি কহব সজনি তাহেরি কহিনী।”
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এর বঙ্গীয় শব্দকোষ অনুযায়ী প্রাকৃত ভাষায় কাহিনির বিবর্তন ঘটেছে এরকমভাবেঃ
কহাণঅ, -ণিআ>কহানি>কহিনি>কাহিনি
@ফরিদ আহমেদ,
মুশকিলে ফালাইলেন। অনলাইন ডিকশনারিতে ‘ story’ লিখা প্রতিশব্দ চাওয়াতে বাইর হৈল এইটা –
[img]http://ovidhan.org/index.php?act=process&o=story&Sec=BNG[/img]
দ্যাখেন, এইখানে রূপকথা, উপকথা উপন্যাস, নাটক প্রভৃতির কাহিনী কইছে।
অনলাইন সংসদ বাংলা ডিকশনারীতে কাহিনি আর কাহিনী দুইটাই সঠিক বলে।
যেমন কাহিনী লিখলে আসে-
ইতিকথা (p. 0136) [ itikathā ] n a tale; a legend; a chronicle; history. ইতিকাহিনী n. same as ইতিকথা ।
তবে আমার লেখায় এতোগুলা বানান ভুল আছে যে, কাহিনি/কাহিনী নিয়া আলগা ফাল না পাড়াই ভালো।
@অভিজিৎ,
অভিধানে থাকলেই শব্দ বানান শুদ্ধ হয় না অভি। আর বানানের ক্ষেত্রে সংসদ বাংলা অভিধানকে আমি খুব একটা নির্ভরযোগ্য বলে মনে করি না। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমীর অভিধান অনেক বেশি স্বস্তিদায়ক। তবে, মজার বিষয় হচ্ছে আমার কাছে বাংলা একাডেমীর ১৯৯৩ সালের একটা English-Bengali Dictionary আছে। সেটাতেও কাহিনীই লেখা আছে। 🙁
আমি বাংলা একাডেমী প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মের কথা এবং তাদের করা বাংলা বানান-অভিধান অনুযায়ীই ‘কাহিনী’ শব্দটিকে ভুল বলেছি। তুমি মানতে না চাইলে সে তোমার ব্যাপার। তোমার মত একজন বিখ্যাত ব্যক্তি এটা লিখতো বলেই এখন থেকে দূর ভবিষ্যতে হয়তো এটা ব্যাকরণে শুদ্ধ বানান বলে গণ্য হয়ে যাবে। মুক্তমনার এই প্রবন্ধটিকেই হয়তো রেফারেন্স হিসেবে দেওয়া হবে। 🙂
বাংলা একাডেমীর প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম প্রকাশিত হয় ১৯৯২ সালে। পরে এর পরিমার্জিত সংস্করণ বের হয় ১৯৯৪ সালে। এই নিয়ম সুপারিশ করার জন্য বাংলা একাডেমী যে সুপারিশ কমিটি তৈরি করেছিল তার সভাপতি ছিলেন প্রফেসর আনিসুজ্জামান। অন্য সদস্যরা ছিলেন প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামা, জনাব জামিল চৌধুরী, অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস এবং জনাব বশীর আলহেলাল। এর ভিত্তিতেই বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয় বাংলা বানান-অভিধান। এর প্রণেতা ছিলেন জামিল চৌধুরী। ৯৪ সালে প্রণীত নিয়মের কিছু অসঙ্গতির প্রেক্ষিতে কিছু সংশোধনী গ্রহণ করা হয় ২০০০ সালে। সেই সংশোধনী কমিটির সদস্য ছিলেন প্রফেসর আনিসুজ্জামান, প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, জামিল চৌধুরী এবং সেলিনা হোসেন।
বাংলা একাডেমী প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মে ই কার ঈ কার সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ
তৎসম শব্দ
[১.০১] তৎসম অর্থাৎ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অবিকৃত সংস্কৃত শব্দের বানান যথাযথ ও অপরিবর্তিত থাকবে। কারণ এইসব শব্দের বানান ও ব্যাকরণগত প্রকরণ ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট রয়েছে।
[১.০২] তবে যে-সব তৎসম শব্দে ই ঈ বা উ ঊ উভয় শুদ্ধ সেইসব শব্দে কেবল ই বা উ এবং তার কারচিহ্ন ি ু ব্যবহৃত হবে। যেমন: কিংবদন্তি, খঞ্জনি, চিৎকার, ধমনি, ধূলি, পঞ্জি, পদবি, ভঙ্গি, মঞ্জরি, মসি, লহরি, সরণি, সূচিপত্র, উর্ণা, উষা।
অ-তৎসম শব্দ অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র শব্দ
[২.০১] ই ঈ উ ঊ
সকল অ-তৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র শব্দে কেবল ই এবং উ এবং এদের – কার চিহ্ন ি ু ব্যবহৃত হবে। এমনকি স্ত্রীবাচক ও জাতিবাচক ইত্যাদি শব্দের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।
এই ২.০১ নিয়মের কারণেই বাংলা একাডেমী তাদের বাংলা বানান অভিধানে পরিষ্কার করেই কাহিনি বানানকে কাহিনি লিখেছে, লিখেছে কাহিনিকার, কাহিনিচিত্র শব্দগুলো। স্ক্যানারের অভাবে তুলে দিতে পারলাম না পৃষ্ঠাটা।
বাংলা একাডেমীর এই বানান নিয়ম কি স্বতন্ত্র কিছু? না তা নয়। বাংলা একাডেমীর বিশেষজ্ঞ কমিটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি, বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক গৃহীত বানানরীতি সবগুলোকেই বিবেচনায় নিয়েছে। সব কিছুর সমন্ব্য় সাধন করেই একটি অভিন্ন বানানরীতি প্রনয়ণ করেছেন তারা। বাংলা বানান বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মাহবুবুল হকও একই কথা বলেছেন। তিনি বলেন, ‘এক সময় বাংলা বানানের সমস্যা ছিল, এখন নেই। বাংলা একাডেমী, পশ্চিমবঙ্গ আকাদেমি, পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রমিত বানানের নিয়ম তৈরি করেছে এবং এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনো বিভেদ নেই।’
কাহিনি নিয়ে আর কোন কাহিনি করার আমারও ইচ্ছে নেই। কাজেই এটিই এ বিষয়ে শেষ মন্তব্য।
হঠাৎ মনে পড়ল অভিজিতের ঠেলা খেয়ে বহুদিন আগে আইনস্টাইনকে নিয়ে দুকলম লিখেছিলাম-সেটাও এই পাঠকদের জন্যে দিয়ে দিলাম
লিংকটা এখানেঃ
এটা অনুর অস্তিত্বের বাস্তব প্রমান হবে।
এটা জি টি আর বা সাধারন আপেক্ষিকতাবাদের তত্ত্বের প্রমান হবে যা এডিংটন করেছিলেন।
স্পেশাল থিওরীর প্রমান এই তত্ত্ব আবিস্কারের আগেই মাইকেলসন মর্লি ১৮৮৯ সালের পরীক্ষার মাধ্যমে পেয়েছিলেন-কিন্ত্ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব না জানা থাকায়, ব্যাখ্যা করতে পারেন নি।
গোটা লেখাটাতে সাধারন আর বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের তত্ত্বকে আলাদা করা উচিত ছিল-নইলে এই ধরনের সমস্যা হবে।
আমাদের বাঙালীদের আইনস্টাইনকে নিয়ে যত মাতামাতি সত্যেন বোস, মেঘনাদ সাহা বা রামন কে নিয়ে সেই তুলনায় খুব কম কাজ হয়েছে। ইনারা যেহেতু আমাদের পরিবেশেই মানুষ হয়েছেন, এদের জীবনী আমাকে ভীষন ভাবে অনুপ্রেরিত করে। মেঘনাদ সাহা ১৯৫০ সালে ভারতের যে প্রথম পাঁচ মেগাটনের সাইক্লোটন বানান নিজেদের ওয়ার্কসপ থেকে, তা চাক্ষুস দেখার পর আমার মনে হয়েছিল, চাকরী ভিত্তিক শিক্ষার ফলে আমরা শুধুই পিছিয়ে গেছি। স্যার রামনের স্পেকট্রোস্কোপ দেখে অবাক হয়েছিলাম-সূর্যের আলোকে ্টেলিস্কপের মাধ্যমে স্পেক্ট্রস্কোপে পাঠাতেন-সেখান থেকেই প্রথম রমন এফেক্ট দেখতে পান-
ছোটবেলায় এদের ওপর লেখা কিছু বাংলা বই দেখেছি। সেগুলো আর বোধ হয় পাওয়া যায় না। এগুলো উদ্ধার করতে হবে বা অভিজিতের মতন বিজ্ঞান লেখকদের উচিত বাঙালী বিজ্ঞানীদের ওপর একটা সিরিজ করা। আমার মতে তা গুরুত্বপূর্ন কাজ হবে।
@বিপ্লব পাল,
হ্যা, আমি আসলে জেনেরাল থিওরী অব রিলেটিভিটিই বোঝাতে চেয়েছি, যদিও সেটা উল্লেখ করা হয়নি।
অন্য মন্তব্যগুলোর জন্য ধন্যবাদ। সত্যেন বোস, মেঘনাদ সাহা বা রামন কে নিয়ে লেখা সলেই দরকার। আমি আমার আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী বইয়ে আলাদা করে জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাদের অবদানের উল্লেখ করেছিলাম। আর এ ছাড়া ছিলেন চন্দ্রশেখর। তার কথাও বলেছি। চন্দ্রশেখর আর এডিংটনের বিখ্যাত বিবাদ নিয়ে আমার একটা লেখা ছিলো এখানে।